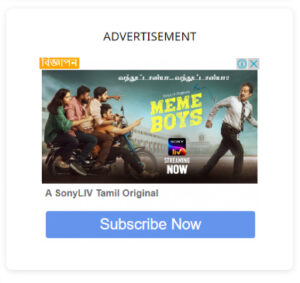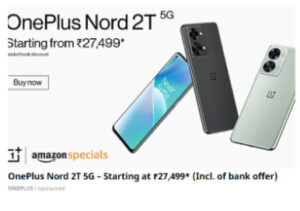- August 13th, 2022
বার্সিলোনা বনাম টালিগঞ্জ অগ্রগামী
সুমন চট্টোপাধ্যায়
সব বিষয়ে ‘ওরা’ দশ গোল দিত, কিংবা আরও বেশি। আমরা (পড়ুন আমি) গায়ের জ্বালা মেটাতাম নিজের পুজো স্যুভেনিরের সম্পাদকীয়তে ওদের নাম না করে বেদম গালি দিয়ে। তা নিয়ে পাড়ায় দিনকতক চর্চা হত, তর্ক-বিতর্ক হত, অক্ষমের প্রাপ্তিযোগ বলতে ওইটুকুই।
আমরা মানে দেওদার স্ট্রিটের বালক সঙ্ঘ, ওরা মানে অদূরে হাজরা রোডের উপর স্থায়ী ক্লাবের মালিক মিলন চক্র। দু’টি পুজোর মধ্যে সামান্য কয়েক পায়ের তফাৎ। পুজো এলে মনে হত ফারাকটা আসমান-জমিন। এখন এতদিন পরে পিছনে ফিরে তাকালে হাসি পায়। তখন রেশারেশির উত্তেজনায় রোমকূপ খাড়া হয়ে থাকত।
কাণ্ডজ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার করলে দু’টি পুজোর তুলনা টানাটাই অর্বাচীনের মতো কাজ। মিলন চক্র সুয়োরানি হলে বালক সঙ্ঘ দুয়োরানির চেয়েও হতশ্রী। বালক সঙ্ঘের পুজো হত সরু, অন্ধ-গলির ভিতর, কারুকার্যহীন ছোট্ট মণ্ডপ, মানানসই একচালার ঠাকুর, মামুলি আলোকসজ্জা। হাজরা রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কেউ যদি ভুল করে অথবা কৌতূহলবশত দেওদার স্ট্রিটে ঢুকে পড়ে, একমাত্র তাহলেই সেই ভাগ্যবান বালক সঙ্ঘের পুজো দেখতে পারে। তেমন ঘটনা ক্কচিৎ ঘটত বলে সন্ধের সময়ে অন্য মণ্ডপে যখন উপচে পড়া ভিড়, বালক সঙ্ঘের সামনে তখন কেবল পাড়ার কাচ্চা-বাচ্চাদের জটলা।
তুলনায় মিলন চক্র কয়েক আলোকবর্ষ এগিয়ে, লোকবলে, অর্থবলে। বড় রাস্তার উপর পুজো, ভিড় টানতে হত না। চন্দননগর ছিল ওদের ঠাঁটবাটের উৎসস্থল। সেখান থেকে মিস্ত্রিরা এসে এমন আলোর কেরামতি দেখাত যে না চেয়ে উপায় থাকত না। সঙ্গে আসত পাহাড়-প্রমাণ প্রতিমা, এত বড় আর এত উঁচু, সামনে দাঁড়ালে নিজেকে লিলিপুট মনে হয়। প্রতিমা নির্মাণে এই আতিশয্য চন্দননগরের ট্রেড মার্ক কিন্তু আমার বিলকুল না-পসন্দ। আমার ব্যক্তিগত পছন্দ ডাকের সাজে একচালা ঠাকুর, প্রতিমা নিয়ে যেমন খুশি তেমন বাঁদরামির আমি ঘোরতর বিরোধী। দর্শন করে ভক্তিই যদি না জন্মাল, আপনা থেকে হাত দুটো কপালে না-ই উঠে এল, তাকে মা দুগ্গা বলে মানতে আমি প্রস্তুত নই।
ঝাড়গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে বাবা ওই দেওদার স্ট্রিটেই একটি সওয়া দু’কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন মাসিক দু’শো টাকায়। যে গলিতে পুজো হত, তারই শেষপ্রান্তে একটি তিনতলা বাড়ির দোতলার পিছন দিকে আমাদের ফ্ল্যাট। পাড়ার দাদারা কী ভাবে যেন আমাকেও জড়িয়ে নিলেন পুজোর আয়োজনের সঙ্গে। দ্বিতীয় বছরেই আমি হাফ-প্যান্ট পরা সেক্রেটারি, পড়ি ক্লাস টেনে। টানা পাঁচ বছর বালক সঙ্ঘের পুজোর মাতব্বর ছিলাম আমি। পাঁচজনকে নিয়ে কী ভাবে চলতে হয়, সংগঠন কী ভাবে চালাতে হয়, তার হাতে-কলমে শিক্ষা হয়েছিল বারোয়ারি পুজো পরিচলনা করতে গিয়েই। ‘জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা’ — ষোলো আনা সত্যি কথা।
বহু আগে বাল্যকাল অন্তর্হিত হওয়া লোকজন যে পুজো করে, কোন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন লোক তার নাম বালক সঙ্ঘ রেখেছিলেন, বলতে পারব না। কবে থেকে পুজোর সূত্রপাত, সেটাও ছিল রহস্যে মোড়া। তখন অনেক বারোয়ারি পুজোর বয়স দেখতাম জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। গত বছর যারা বলেছিল দ্বাবিংশতি বছর, এ বার তারাই বলছে আমাদের হীরক জয়ন্তী। আমাদের অবশ্য বয়স ভাঁড়ানোর প্রয়োজনই ছিল না, পুজো তো হবে যথাপূর্বং তথাপরং।
বালক সঙ্ঘের সভাপতি হিসেবে বছর বছর একটাই নাম ছাপা হত — ধীরেন দে, দে’জ মেডিক্যালের মালিক, মোহনবাগান ক্লাবের সর্বময় কর্তা। দেওদার স্ট্রিটের চেহারাটা অনেকটা ঘোড়ার ক্ষুরের মতো, একটি শাখায় প্রকাণ্ড পাঁচিল দিয়ে ঘেরা অট্টালিকায় বাস করতেন মালিককুল। ধীরেনবাবু কোনও দিন ভুল করেও পুজো দেখতে আসেননি, পুজো নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথাও ছিল না। শুধু পুজোর আগে একটি দিন আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তাঁর সন্দর্শনে যেতে হত, তিনি তিনটি কড়কড়ে একশ টাকার নোট আমাদের হাতে তুলে দিয়ে পত্রপাঠ বিদেয় করে দিতেন। আজ তিনশো টাকায় এক প্যাকেট ভালো ব্র্যান্ডের সিগারেট মেলে না বোধহয়, সত্তর দশকের গোড়ায় কিন্তু সেটা ছিল অনেক টাকা। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়ে ধীরেনবাবুর এক ভাইপোর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। রাণা। আমার মতো সে-ও ১৬ নম্বর সরকারি বাসে উঠত একই স্টপেজ থেকে। বড়লোক বাড়ির ছেলে, তবু গাড়ি চড়ে কলেজ যাওয়াকে সে অপরাধের পর্যায়ে ফেলত। মা লক্ষ্মীকে কিঞ্চিৎ আড়ালে রেখে সরস্বতীর সাধনা, এটাই ছিল আমাদের প্রজন্মের যুগমন্ত্র।
মিলন চক্রের অন্তরালবাসিনী প্যাট্রন ছিলেন সুচিত্রা সেন। তাঁর নাম ব্যবহার করা যেত না, মণ্ডপে আসার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর বাড়িটিও ছিল আমাদের পাড়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে, সায়েন্স কলেজের বিপরীতে। মিলন চক্রের মাথা প্রদীপদা’র সঙ্গে সুচিত্রা সেনের কী ভাবে যেন ভালো পরিচয় ছিল। পেটে কামান মারলেও প্রদীপদা এ নিয়ে মুখ খুলতেন না। তবে প্রতি পুজোর আগে ঠিক চুপিসাড়ে গিয়ে গ্রেটা গার্বোর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে আনতেন। সুচিত্রা সেনের মতো না হলেও মিলন চক্রের এমন বেশ কিছু বড়লোক পৃষ্ঠপোষক ছিল, আর আমাদের সবেধন নীলমণি ধীরেন দে। লড়াইটা এখানেই অসম হয়ে যেত, ভাঁড়ে যার মা ভবানী তার কি ঠাঁটবাটের সাধ্য থাকে?
পাড়ার দাদারা গোড়ার দিকে আমায় চাঁদাপার্টিতে ভিড়িয়ে দিয়েছিল। সপ্তাহে কাজের দিনগুলোয় সন্ধেবেলা, রবিবার দু’বেলাই। লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে ফি-সন্ধ্যায় পকেটে পেন হাতে রশিদের বই নিয়ে দরজায় দরজায় কড়া নাড়া সম্ভব ছিল না। অচিরেই বুঝলাম ব্যাপারটা চূড়ান্ত অসম্মানের। বেল বাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ডাকাত এসেছে ভেবে গেরস্ত আর দরজাই খোলে না। কেউ আবার চাঁদার কথা শুনেই সপাটে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়। বেশির ভাগই কাক তাড়ানোর ঢঙে পরে আসতে বলে। গোটা পাড়ায় হাতে গোনা কয়েকটি পরিবারের সন্ধান পেয়েছিলাম যারা সুভদ্র, সজ্জন, বসার ঘরে ঢুকতে দিয়ে চেয়ারে বসতে দেয়, এমনকী চা খেতেও অনুরোধ করে। আমার বাদশাহি মেজাজ, চাঁদা তুলতে গিয়ে কয়েক জায়গায় হাতাহাতি লেগে যায় আর কী! পাড়ার দাদাদের বললাম, চাঁদা তোলা আমার কম্মো নয়। আমি বরং দু’চারটে বিজ্ঞাপন আনার চেষ্টা করি।
এ কাজে আমার সবচেয়ে বড় সহায় ছিলেন আমার ছোটকাকা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি স্টিল অথরিটিতে মস্ত বড় পদে চাকরি করতেন। ছোটকাকার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, কাকা-ভাইপোর মাঝখনে কোনও দেওয়াল নেই। এমনিতেই বছরে বেশ কয়েকবার স্রেফ আড্ডা মারতে ছোটকাকার অফিসে ঢুঁ মারতাম, পুজোর আগে বারেবারে। এক গোছা ফর্ম কাকার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলতাম, তুমি না দেখলে পাড়ায় কিন্তু আমার প্রেস্টিজে গ্যামাক্সিন। ঠিক পুজোর মুখে মুখে কাকা চেক-সহ ফর্মগুলি ফেরত দিতেন। সেদিন আমি গলিতে ঢুকতাম কলার তুলে। কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে অ্যারিস্টোক্রেসির কুলীন কুলে আমার পরিচিতি বাড়ল, বাড়ল পুজোর সময়ে বিজ্ঞাপনও, সরকারি এবং বেসরকারি। একটা সময়ে দেখা গেল পুজো তহবিলে আমার একক অবদান ধীরেন দে-র তুলনায় অনেক গুণ বেশি। বারোয়ারি পুজোর একটা অলিখিত নিয়ম হল, মাল যার ক্ষমতা তারই। যে গোরু দুধ দেবে, তার লাথিও সই। আমি ছিলাম বালক সঙ্ঘের সেই দুধেল গোরু। দুঃখ একটাই, মিলন চক্রকে একটিবারও হারাতে পারিনি।
আমি চিরটাকালই ওই আন্ডারডগেদের দলে।




 Arts and Literature
Arts and Literature Bioscope
Bioscope Columns
Columns Green Field
Green Field Health World
Health World Interviews
Interviews Investigation
Investigation Live Life King Size
Live Life King Size Man-Woman
Man-Woman Memoir
Memoir Mind Matters
Mind Matters News
News No Harm Knowing
No Harm Knowing Personal History
Personal History Real Simple
Real Simple Save to Live
Save to Live Suman Nama
Suman Nama Today in History
Today in History Translation
Translation Trivia
Trivia Who Why What How
Who Why What How