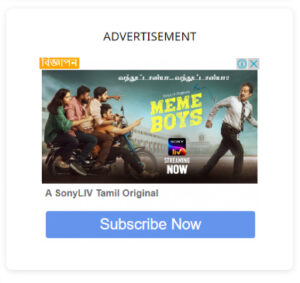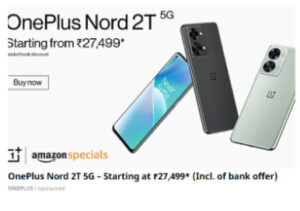- August 17th, 2022
বুদ্ধং শরণং (পর্ব-১১)
সুমন চট্টোপাধ্যায়
নিজেকে বদলে ফেলার কাজটা আদৌ সহজ নয় এটা যেমন সত্যি তেমনি একই রকম সত্যি এই প্রবাদটিও যে স্বভাব যায় না মলেও। ফলে মাঝেমাঝেই সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় বুদ্ধদেবের মুখ থেকে এমন সব মন্তব্য বেরিয়ে আসত যা তাঁর পুরোনো অবতারের কথা মনে করিয়ে দিত, মুহূর্তের জন্য হলেও বিভ্রম হতো মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তনটা আসল না নকল, কোনটা তাঁর মুখ কোনটাই বা মুখোশ।
সিঙ্গুর আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া পর্যন্ত বুদ্ধবাবু কথা-বার্তায় অনেক সময়ই সংযম হারিয়ে ফেলতেন। যেমন ধরা যাক তাঁর সেই চূড়ান্ত দাম্ভিক আস্ফালন, ‘আমরা ২৩৫ আর ওরা মোটে ৪৫’। কিংবা নন্দীগ্রামে তথাকথিত সূর্যোদয়ের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর গায়ের জ্বালা জুড়োনো মন্তব্য, 'দে হ্যাভ বিন পেড ব্যাক ইন দ্য সেম কয়েন।’ কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন স্লোগান শুনে তাঁর কটাক্ষ, 'মা, মাটি, মানুষ যাত্রাপালার নাম হতে পারে, ভদ্র রাজনৈতিক দলের স্লোগান হয় কী করে?’ পরবর্তীতে এই সব মন্তব্যই বুনো ষাঁড় হয়ে তাঁকে তাড়া করে বেরিয়েছিল, হয়ে উঠেছিল বিরোধীদের প্রচারের অস্ত্র।
বুদ্ধবাবুর মুখ্যমন্ত্রিত্বকে অনায়াসে দু’টি পর্বে ভাগ করে ফেলা যায়, প্রথম পর্বে তিনি স্বপ্নের সওদাগর, দ্বিতীয় পর্বে ব্রুডিং কিং লিয়ার। আমার কাছে প্রথম পর্বটি দারুণ উপভোগ্য ছিল। দ্বিতীয় পর্বে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিজের রাজ্যের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নাগরিক হিসেবে আমাকে পীড়িতই করেছিল। আরও বেশি করে এই কারণে যে তাঁর গন্তব্য এক্কেবারে সঠিক ছিল, কিন্তু ভুল রাস্তা ধরার জন্য সেখানে তিনি পৌঁছতে পারেননি। বুদ্ধদেবের ব্যর্থতার মাশুল আজ রাজ্যকে ভয়ানক ভাবে গুনতে হচ্ছে, আরও কতকাল গুনতে হবে সেটাও অনিশ্চিত।
সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র, এর চেয়েও বড় একটা পরিচয় আছে বুদ্ধবাবুর। যে কথা অনেকেই জানে না, ফলে আলোচনাও হয় না একেবারেই। সেটা হল, বুদ্ধবাবুর পিতৃদেব ‘পুরোহিত তর্পণের’ রচয়িতা, পূজারিদের কাছে যা প্রায় বাইবেলের মতো মর্যাদা পায় এবং পুজোর কাজে যা একেবারেই অপরিহার্য। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধবাবু ছিলেন আইএসও সার্টিফায়েড নাস্তিক। অনেক চেষ্টা করেও এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা বেশি দূর এগোতে পারিনি। পশ্চিমবঙ্গের পৌরোহিত্যের দায়িত্ব পাওয়ার পরে তিনি একটি মন্ত্রই ক্রমাগত আউড়ে চলতেন- শিল্পায়ন। বাকি অনেক বিষয়ে তাঁর ছুঁৎমার্গ ছিল, পছন্দ এবং অপছন্দ দুটোই চড়া তারে বাঁধা, একমাত্র ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের মধ্যে তিনি কোনও তারতম্য বিধান করতেন না। বাংলায় এসে যিনিই বিনিয়োগ করবেন, তাঁকেই লাল সেলাম। অনেকটা যেন দেং শিয়াও পিংয়ের দর্শনের মতো, বিড়ালের গাত্রবর্ণ দেখার কোনও প্রয়োজন নেই আমার, যতক্ষণ সে ইঁদুর ধরতে পারছে।
পশ্চিমবঙ্গকে শিল্প-শ্মশানে পরিণত করার ঐতিহাসিক দায় যে তাঁদের কাঁধেই বর্তায় বুদ্ধবাবু ব্যক্তিগত স্তরে তা অকপটে স্বীকার করতেন। বিশ্বাস করতেন জঙ্গি, মারমুখী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করে আখেরে কারও লাভ হয়নি, একটির পর একটি শিল্প বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছে, তজ্জনিত দুর্নাম এমন ভাবে পশ্চিমবঙ্গের নামের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে যে কোনও বড় শিল্পপতি আর রাজ্যটির দিকে ফিরেও তাকান না। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক মাশুল সমীকরণ নীতি বাংলাকে পিছিয়ে দিয়েছিল, এই তত্ত্ব আংশিক সত্য, তার বেশি কিছু নয়। আমার অনেক সময় মনে হয়েছে, বুদ্ধবাবু বোধহয় পূর্বসূরিদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। সে জন্যই দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী পারতপক্ষে দলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন, ধর্মঘট আর বনধের কার্যকারিতা নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলতেন, আর মাঝেমাঝেই বিরক্তি প্রকাশ করে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলতেন, ‘বোঝেনই তো আমাদের দলটা কী রকম।’
এ রাজ্যে শিল্পায়নের সঙ্গে বুদ্ধবাবুর নামটা একই বন্ধনীতে উচ্চারিত হলেও, ঐতিহাসিক সত্যটি হল রাজ্য প্রশাসনের কাজের অভিমুখ শিল্পের দিকে ঘোরানোর সূচনাটি করেছিলেন জ্যোতি বসু ও সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা না করেই ১৯৯৪ সালে জ্যোতিবাবু রাজ্য বিধানসভায় যে নতুন শিল্পনীতি পেশ করেন সেটাই প্রথম স্পষ্ট করে দেয় বাঘ তার ডোরা বদল করছে। এই নীতিতে বেসরকারি পুঁজির সঙ্গে এই প্রথম রাজ্যে বিদেশি পুঁজিকেও স্বাগত জানানো হয়। গুরুত্ব দেওয়া হয় পরিকাঠামোর উন্নতির ওপর। বলা হয়, শিল্প-বিবাদ মেটাতে হবে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে। মার্কসবাদীদের চিরাচরিত শত্রু যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনই হয় এই মোড় ঘোরানো শিল্পনীতির মূল কথা। নতুন শিল্প-প্রস্তাব এলে দ্রুত তাকে ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য তৈরি হয় ১১ জনের উচ্চপদস্থ কমিটি। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাথায় বসানো হয় সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। গোটা ভারতবর্ষে অচিরেই এই বার্তাটি পৌঁছে যায়, বঙ্গজ কমিউনিস্টরা আর পুরোনো নীতি, আদর্শ, বিশ্বাস আঁকড়ে থাকতে চান না, উদারীকরণের নয়া জমানায় তাঁরা নতুন পথে হাঁটতে চান। নতুন শিল্পনীতি পেশের সুফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল তা নয়, কেন না সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে মানুষের মনে গেঁথে যাওয়া নঞর্থক ধারণাটি বদল করা। আর সেটা ছিল বিনা অক্সিজেনে এভারেস্টে ওঠার মতো কঠিন কাজ।
জ্যোতিবাবু নতুন শিল্পনীতি পেশের পরে প্রত্যাশিত ভাবেই শরিক দলগুলি রে রে করে উঠেছিল। আরএসপি-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে কোনও আগাম আলোচনা করা হয়নি। সুতরাং এটা সিপিএমের শিল্পনীতি, বামফ্রন্টের নয়। ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক চিত্ত বসুর ব্যাখ্যা ছিল, বেসরকারি আর বিদেশি পুঁজি এলেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই। এই নীতি পেশের পরে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যটা রইল কোথায়? সিপিএমের অন্দরেও ফিসফাস শোনা যাচ্ছিল, কেউ কেউ বলেছিলেন রাজ্য সম্মেলনে জ্যোতিবাবুর এই শিল্পনীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। অথচ হল তার উল্টোটা, গোটা দল এককাট্টা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর পাশে। এমনকি সিটু নেতারাও বললেন নতুন শিল্পনীতিতে তাঁরা আপত্তিকর কিছু দেখছেন না।
ফল মিলতে শুরু করল ১৯৯৪ সালেই। মার্কিন মুলুক থেকে এক অখ্যাত বঙ্গসন্তান কলকাতায় পদার্পণ করে ঘোষণা করলেন, তিনি হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসে ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে উৎসাহী। প্রাথমিক সমঝোতাপত্র সই হল চার শরিকের মধ্যে- রাজ্য সরকার, টাটা গোষ্ঠী, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এবং চ্যাটার্জি গ্রুপ। সেই বঙ্গসন্তানকে আজ সব্বাই এক ডাকে চেনে। পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ওরফে পি সি।
হলদিয়ার অগ্রগতির ইতিহাস খুবই কর্দমাক্ত, এখানে তার বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। বামফ্রন্ট সরকারের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পূর্ণেন্দু মাতৃভূমিতে এলেও পরবর্তী কালে শেয়ার কেনা-বেচা নিয়ে তাদের সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে ওঠে। ক্ষমতায় আসার পরে নিজে উদ্যোগ নিয়ে মমতা এই জট ছাড়িয়ে দেন। তারপর থেকে হলদিয়াকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি, এটি এখন দারুন লাভজনক সংস্থা।
পূর্ণেন্দু কলকাতায় আসা ইস্তক আমি তাঁকে চিনি, ধীরে ধীরে সেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। তারই সুবাদে কারখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিনে আমার এমন এক অভিজ্ঞতা হয় যা আমার কর্মজীবনে আর কখনও হয়নি। কলকাতা থেকে রতন টাটাকে হলদিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্ণেন্দু একটি হেলিকপ্টার ভাড়া করেন। স্থির হয় অসীম দাশগুপ্ত রতনের সঙ্গী হবেন। ঠিক তার আগের রাতে পূর্ণেন্দু বললেন, ‘ইচ্ছে করলে তুমি রতন টাটার সঙ্গে হেলিকপ্টারে আসতে পারো, আমাকে ভোরবেলা যেতে হবে, আমি থাকতে পারছি না।’ আমি কি এত বড় আহাম্মক যে এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া হতে দেব?
নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই আমি পৌঁছে গেলাম, রতন টাটাকে সঙ্গে নিয়ে অসীমবাবু এলেন ঠিক সময়ে। বুঝতে পারলাম এই হেলিকপ্টারে আমিও যাত্রী হব, অসীমবাবু তা আগে থেকেই জানেন, পূর্ণেন্দু জানিয়ে দিয়েছিলেন সম্ভবত। তিনিই রতন টাটার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন, আমরা হাত মেললাম।
হেলিকপ্টারের ভিতরে এমনিতেই এমন আওয়াজ হয় যে কথা বলার কোনও উপায় থাকে না। আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই দেখি রতন টাটা নিজের আসন ছেড়ে ককপিটে গেলেন, তারপর বসে পড়লেন চালকের আসনে। আমি আর অসীমবাবু বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম, আমার একটু ভয়ও লাগল। কিন্তু চালক নির্বিকার, মনে হচ্ছে যেন হেলিকপ্টার চালানোই তাঁর কাজ। হলদিয়ায় অনুষ্ঠানস্থলের অদূরে তৈরি হেলিপ্যাডে নির্বিঘ্নে আমরা অবতরণ করলাম। চালক রতন টাটা, যাত্রী আমি দু’পয়সার কলমচি, সত্যি এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি। (চলবে)




 Arts and Literature
Arts and Literature Bioscope
Bioscope Columns
Columns Green Field
Green Field Health World
Health World Interviews
Interviews Investigation
Investigation Live Life King Size
Live Life King Size Man-Woman
Man-Woman Memoir
Memoir Mind Matters
Mind Matters News
News No Harm Knowing
No Harm Knowing Personal History
Personal History Real Simple
Real Simple Save to Live
Save to Live Suman Nama
Suman Nama Today in History
Today in History Translation
Translation Trivia
Trivia Who Why What How
Who Why What How