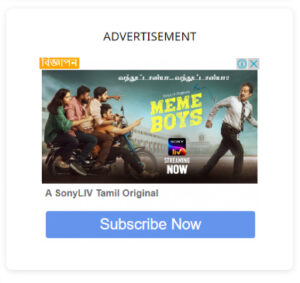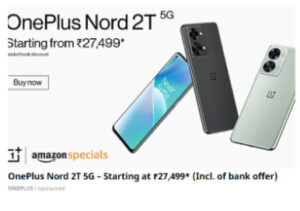- August 13th, 2022
পূর্ণকুম্ভ, শূন্য মন
পূর্ণকুম্ভ, শূন্য মন
সুমন চট্টোপাধ্যায়
(প্রথম পর্ব)
১৩৯২-এর ২৬ শে চৈত্র। খ্রিস্টাব্দের হিসেবে ১৯৮৬-র ৯ এপ্রিল। চৈত্র-অমাবস্যার সন্ধে নেমেছে হর-কি-পিয়ারির ঘাটে। চলছে গঙ্গা-আরতির প্রস্তুতি। গঙ্গার দুপারে বাঁধানো নদীতটে থই থই পুণ্যার্থীর ভিড়। কোনও মতে একটা পাকাপোক্ত প্যাকিং বাক্সের উপরে ১০ টাকা দক্ষিণা দিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছি আমরা চারজন— ‘কালকূট’ সমরেশ বসু, তাঁর স্ত্রী ধরিত্রী বসু (টুনি বৌদি), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আর আমি। পাতার ভেলায় ভাসানো জ্বলন্ত মাটির প্রদীপের আলোয় চিকচিক করছে কালো গঙ্গার কুলুকুলু ঘৃত-দীপ। জলের বুকে প্রতিবিম্ব পড়ে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে প্রদীপের সংখ্যা। ঘাটের গুঞ্জনের মধ্যে হঠ্ হঠ্ চিৎকার: ‘গেল গেল, ভেসে গেল।’ হাতের চেন ফস্কে ভেসে গেছে সাঁতার না জানা, অজানা, অনামী এক কিশোর। তাকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দিল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হলদে পোশাক পরা সাঁতারুরা। আর্তরব শুনে পাশে বসা সমরেশদা আমাকে বললেন, ‘আমি যদি এখানে মরে যাই, এই গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়ে দিও। জীবন-মৃত্যুর নিরন্তরতা এই নিরন্তর স্রোতে বয়ে চলেছে। আমিও চলে যাব।’
যে কোনও দিন চলে যেতে হবে, ‘কালকূট’ সমরেশদা তা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন, ‘বুকে তার ছোবলের ঘা লেগেছিল যে।’ তবু নিজেই কালকূট যিনি, বিষ তাঁকে কাবু করবে কী করে? ডাক্তার-বদ্যি, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, সকলের সাবধানবাণীকে থোড়াই কেয়ার করে তিনি আবার অমৃত কুম্ভের সন্ধানে হরিদ্বারের গঙ্গাদ্বারে আসর নিয়েছিলেন। গ্রহণ করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার হয়ে পূর্ণ কুম্ভে তাঁর অভিযাত্রার রোজনামচা লেখার অনুরোধ। আমার কাজ ছিল নিজের প্রতিবেদন লেখার পাশাপাশি সমরেশদাকে সঙ্গ দেওয়া আর তাঁর লেখাগুলোকে রোমান হরফে রূপান্তরিত করে টেলেক্সের মাধ্যমে যথাসময়ে কলকাতার অফিসে পাঠানো। প্রয়াগ থেকে হরিদ্বারের মাঝখানে শরীর ভেঙে গিয়েছিল কালকূটের, কিন্তু মন ভাঙেনি।
তার বত্রিশ বছর আগে প্রয়াগের সঙ্গমে কালকূট যখন প্রথম অমৃত কুম্ভের সন্ধানে গিয়েছিলেন, তখন আমার জন্ম হয়নি। তবে তাঁর নাম জানতাম সেই শৈশবকাল থেকেই। ‘বি টি রোডের ধারে’ দিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাহিত্যিক পরিচয়। ওই সাড়া জাগানো উপন্যাসের একটা কপি সমরেশ বসু নিজে স্বাক্ষর করে উপহার দিয়েছিলেন আমার বাবাকে। জগদ্দল মিল-মজুরদের কলোনিতে হোগলার ছাউনি দেওয়া ঘরে বন্ধু সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে আমার বাবারও আনাগোনা ছিল। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছিলাম, সমরেশ বসুর যৌবনের সেই সংগ্রামী দিনগুলির কথা। যখন তিনি নৈহাটি লোকালে চেপে গল্প ফিরি করতে আসতেন কলকাতায়। গল্প বিক্রি হলে দু-মুঠো খাওয়া, না হলেও কুছ পরোয়া নেই। হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে বাঁশিতে ফুঁ দিতেন তিনি। কানের পর্দা ফাটানো সাইরেন ছাপিয়ে উঠত সেই বাঁশির সুর।
আর সমরেশ বসুকে প্রথম চাক্ষুষ দেখি, হোগলার ছাউনি ছেড়ে তখন তিনি উঠে এসেছেন দক্ষিণ কলকাতার সার্কাস রেঞ্জের দু-ঘরের ছিমছাম ফ্ল্যাটে। কাকভোরে তখন আমার সহকর্মী, সমরেশবাবুর অসুস্থ জামাতাকে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে। বাইরের ঘরে বসে লিখছিলেন সমরেশ। বহিরাগতের আবির্ভাবে সাতসকালে তাঁর ফ্ল্যাট কেন কলবর-মুখর হয়ে উঠল, তার খোঁজ নিতে অল্পক্ষণের জন্য বেরিয়েছিলেন মাত্র একবার। জামাইয়ের জন্য ডাক্তার ডাকার পরামর্শ দিয়ে আবার মগ্ন হয়েছিলেন লেখায়। পরে সমরেশদার মুখেই শুনেছিলাম, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, তিনি লেখেন। আর লেখেন যখন, থাকেন কল্পনার জগতে। তখন চারদিকে কী হচ্ছে, কে কী বলছে, কে কী করছে, তা তাঁর খেয়াল থাকে না। গোলামি না করলেও লেখাকেই তাঁর জীবিকা করেছিলেন কালকূট। এবং সে জন্য মনে-মনে তাঁর গর্বও ছিল দারুণ। বার বার বলতেন, ‘চাকরি না করেই তো দিব্যি জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, কী বলো?’
বটেই তো। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঠিকই লিখেছেন। মাস-মাইনের ধরা-বাঁধা জীবনকে অবলীলায় এড়িয়ে গিয়ে শুধু বাংলা ভাষায় লিখে সংসার চালানোর চেষ্টা যে দুঃসাধ্য হলেও অসাধ্য নয়, সমরেশ বসু তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। তাই বলে মাঝে-সাঝে তিনি যে কোনও সংবাদপত্রের বিশেষ অ্যাসাইনমেন্টে গ্রহণ করেননি, তা নয়।
১৯৫৪ সালে প্রয়াগের সঙ্গমে পূর্ণকুম্ভে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন আনন্দবাজারের প্রয়াত কানাইলাল সরকার। বত্রিশ বছর পরে অভীক সরকার যখন তাঁকে একই প্রস্তাব দিলেন, শরীর-টরিরের কথা সব ভুলে গিয়ে কালকূট তা লুফে নিয়েছিলেন। আবার পরক্ষণেই তাঁর মনে হয়েছিল, সাগরময় ঘোষ ক্ষুণ্ণ হবেন না তো? ‘জানো তো, অভীকটা ভীষণ চালাক। ‘দেশ’ বলার আগেই আমাকে বলে দিল, আপনি যাবেন এবং শুধু আনন্দবাজারের জন্যই লিখবেন। সাগরদা কী মনে করলেন কে জানে!’ নাস্তিক, অধার্মিক কালকূট সাগরদাকে ভক্তি করতেন ভক্তের মতোই। সাগরদা মোটেই ক্ষুণ্ণ হননি। দেশ পত্রিকার হয়ে তিনি কুম্ভে পাঠিয়েছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে। আর আমাদের দু’জনকেই বার বার বলে দিয়েছিলেন, ‘সমরেশ কিন্তু বড্ড বেপরোয়া। ওকে চোখে চোখে রেখো।’ (চলবে)




 Arts and Literature
Arts and Literature Bioscope
Bioscope Columns
Columns Green Field
Green Field Health World
Health World Interviews
Interviews Investigation
Investigation Live Life King Size
Live Life King Size Man-Woman
Man-Woman Memoir
Memoir Mind Matters
Mind Matters News
News No Harm Knowing
No Harm Knowing Personal History
Personal History Real Simple
Real Simple Save to Live
Save to Live Suman Nama
Suman Nama Today in History
Today in History Translation
Translation Trivia
Trivia Who Why What How
Who Why What How