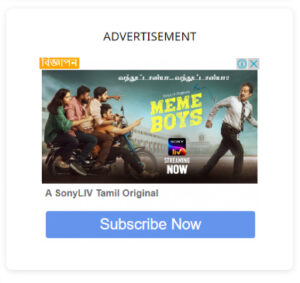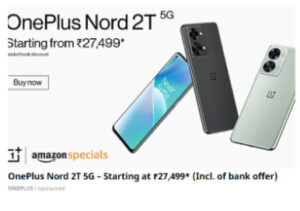- August 13th, 2022
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর
সুমন চট্টোপাধ্যায়
‘পথের নেশা আমায় ডেকেছিল
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।
সূর্য তখন পূর্ব -গগন মূলে
নৌকাদুটি বাঁধা নদীর কুলে
শিশির তখন শুকায়নি তো ফুলে
মন্দিরেতে উঠল বেজে শাঁখ।
পথের নেশা আমায় ডেকেছিল
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।
কবিতাটির নাম ভুলে বসে আছি, ঠিক যেমন এর পরের স্তবকগুলিও আর মুখস্থ নেই। স্পষ্ট যা মনে আছে তা হল, বাবা আমায় অনেক যত্ন করে কবিতাটি আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন, রবীন্দ্র আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নেব বলে। আমরা তখন ঝাড়গ্রামে থাকি, বাবা স্থানীয় সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেন। আমি বোধহয় পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। কুমুদকুমারী হাই ইস্কুলে।
বেনে-বনে শেয়াল রাজা হয়, রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি আর গানে সেই মফঃস্বলের ইস্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারত না। বাবা শেখাতেন আবৃত্তি, মা গান। একবার ইন্টার-স্কুল কোনও গানের প্রতিযোগিতায় মায়ের শেখানো ‘এই কথাটি মনে রেখ’ গেয়ে আমি খুব হাততালি পেয়েছিলাম। সে বড় সুখের সময় ছিল, চির-সবুজ কৈশোর।
আমাদের আটপৌরে জীবন-যাপনে বাহুল্যের লেশমাত্র ছিল না, মানে তা ছিল আমার পিতৃদেবের সাধ্যের অতীত। ফলে বাবা অধ্যাপক হলেও বাড়িতে বইয়ের আলমারি বলে কিছু ছিল না, বসার ঘরের তাকে বই বলতে ছিল বাবার কিছু ইতিহাসের বই, সামান্য কয়েকটি বাংলা গল্প-উপন্যাস আর রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষে বিশ্বভারতী প্রকাশিত সুন্দর চামড়ার বাঁধাই করা দশ-খণ্ডের রবীন্দ্র-রচনাবলী। দেওয়ালের সবচেয়ে ওপরের তাকে তা পরপর সাজানো থাকত, বাবার যক্ষ্মের ধন, আমার বা দিদির সাহস হতনা রবীন্দ্র রচনাবলীতে হাত বোলানোরও। ওটা বাবার সম্পত্তি, প্রায় বিগ্রহের মর্যাদাসম্পন্ন। পড়ার বইয়ের বাইরের বই আমরা নিয়ে আসতাম ইস্কুল আর স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরি থেকে। রবি ঠাকুরের চেয়েও তখন আমাকে অনেক বেশি টানত স্বপন কুমারের রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ, বাড়িতে এনে পড়লে বাবার উত্তম-মধ্যম খাওয়ার ভয় ছিল তাই সিরিজের চটি বইগুলো লাইব্রেরিতে বসেই এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতাম। গোয়েন্দার নাম দীপক আর তার স্যাঙাত রতনলালের সে কি দুর্ধর্ষ কাণ্ড-কারখানা। ফেলুদা তখনও বাজারে নামেনি, শরদিন্দু কিংবা জেমস হেডলি চেজ এসেছিলেন অনেক পরে, বখাটেপনা ছেড়ে আমি ধীরে ধীরে গুডবয় হওয়ার সময়।
রবীন্দ্রচ্ছায়ে আশৈশব লালিত হওয়ার সূচনাটা তার মানে আমার হয়েছিল বাবা-মায়ের হাত ধরেই। নিজের মায়ের কথা বলতে একটু বোধো বাধো তো ঠেকবেই, তবু নির্মম সত্যটা হল সংস্কারগ্রস্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারের নানা টানাপোড়েন, বাধা-বিপত্তি পার হয়ে মা তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগই পাননি। পেলে কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের নামটিও বোধহয় সুচিত্রা মিত্র, কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা নীলিমা সেনের সঙ্গেই এক বন্ধনীতে উঠে আসত। এটা পুত্রের অতি-কথন নয়, মায়ের গলায় রবীন্দ্র-গান শোনা নানা বিশিষ্টজনের সুচিন্তিত অভিমত। তাঁদের মধ্যে একজন সন্তোষ কুমার ঘোষ, আমার বাবার আশৈশব বন্ধু এবং আপাদমস্তক রবীন্দ্র-পূজারিদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর কথায় আসছি পরে, আগে ঘরের পাগলের কথাটুকু সেরে ফেলি।
প্রাতিষ্ঠানিক সঙ্গীত-চর্চার সুযোগ মা কখনও পাননি। একসময় কলকাতায় কিছুদিন অরবিন্দ বিশ্বাসের কাছে শিখেছিলেন, পরে কৃষ্ণনগরে থাকার সময় স্থানীয় একটা গানের স্কুলে যেতেন সপ্তাহে হয়তো একবার। কিশোরকুমার যেমন গান শিখে গায়ক হননি, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমার মা-ও ছিলেন তাই। তাঁর প্রতিভা ছিল জন্মগত, ফলে তাঁর গলায় সুর বসত সরস্বতীর জাদুমন্ত্রে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর এবং বাণী যে একই রকম গুরুত্বপূর্ণ মা সেটা বুঝতেন, দু’য়ের মেল-বন্ধনে তাঁর গলার গান এমন স্বর্গীয় মাত্রায় পৌঁছত, যিনি শুনতেন তিনিই মুগ্ধ হতেন। আমার তো মাঝেমাঝেই মনে হয়, মায়ের জন্মই হয়েছিল কেবল রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি বিধাতার কৃপা-বঞ্চিত ছিলেন, ব্যক্তিগত পরিচিতমন্ডলীর ছোট্ট সীমানার বাইরে তাই তিনি পা রাখারই আর সুযোগ পেলেন না।
আমাদের বাড়িতে ছেলেবেলায় বিনোদনের বস্তু বলতে ছিল একটা ঢাউস সাইজের এইচ এম ভি রেডিও, এমনকী একটা কলের গানও নয়। তখন আকাশবাণীর পক্ষ থেকে প্রতি- সপ্তাহে ‘বেতার জগৎ’ প্রকাশিত হত, তাতে সপ্তাহের সাতটি দিনের সব অনুষ্ঠান ছাপা হত।সকাল ৬টায় বন্দে মাতরম থেকে মাঝরাতের জন-গণ-মন পর্যন্ত। পত্রিকাটি বাড়িতে আসা মাত্র মা সেটা বগলদাবা করতেন, তারপর পেন অথবা পেন্সিল দিয়ে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, আর রজনীকান্তের গানের অনুষ্ঠানগুলোর ওপরে টিক মেরে রাখতেন যাতে পাতাটা খুললেই সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে। আকাশবাণীতে তখন দু’টো স্টেশন ছিল, ‘কলকাতা ক’ আর ‘কলকাতা খ’। বিবিধ ভারতী এল তার বেশ কিছুকাল পরে। টিক মারা একটা অনুষ্ঠান শুনতেও মা ভুল করতেন না, তা বাকি পৃথিবী রসাতলে গেলেও। রেডিওটা ছিল শোয়ার ঘরে, সেখান থেকে রান্নাঘর যেতে হত কিছুটা উঠোন পেরিয়ে। মা রান্নাঘরে থাকলে গান চলত ফুল ভল্যুমে, আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে যেত। মাকে গিয়ে অনুযোগ করে কোনও লাভ হত না, তিনি এক কান দিয়ে কথাটা শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিতেন। এই নিয়মের ব্যত্যয় হত কেবল ছেলে-মেয়ের পরীক্ষার সময়ে। তখন মা একটা টুলের ওপর বসে এক্কেবারে রেডিওর গায়ে কান দিয়ে বসে থাকতেন। মাঝেমাঝে আমার মনে হত এমন অস্বাভাবিকতা মায়ের একটা ব্যাধি। রবীন্দ্রানুরাগের এমন অবিশ্বাস্য নজির আমাদের বাড়িতে তৈরি করেছিলেন আমার মা।
অন্তত হাজার খানেক রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা ও সুর মায়ের কণ্ঠস্থ ছিল, সুর-তাল-লয়ে বিন্দুমাত্র ভুল হলে মা সঙ্গে সঙ্গে তা ধরে ফেলত। এমন একটা ঘরোয়া পরিবেশে বড় হওয়ার সুবাদে সেই সব গানের বেশিরভাগ দিদি আর আমারও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এত দিন পরে এখনও আমি শ’পাঁচেক রবীন্দ্রসঙ্গীত গীতবিতানের সাহায্য না নিয়েও গেয়ে দিতে পারি অনায়াসে। মা অথবা কোনও মাস্টারমশায়ের সামনে হারমোনিয়ম নিয়ে বসে নিয়মিত চর্চা করা বা গলা সাধার বান্দা আমি ছিলাম না, আশৈশব আমি নিয়ম অথবা শৃঙ্খলার বাইরে থাকতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেছি। ছেলেবেলায় আমার গানের গলাটা বোধহয় মন্দ ছিল না, তারপর ধারাবাহিক ধূমপান এবং যাবতীয় অনিয়ম করতে করতে তার হাল এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে যে পাঁচজনের সামনে গাইতে সাহসই হয় না আর। তবু মায়ের কল্যাণে রবীন্দ্রগানের প্রতি অনুরাগ এখনও পর্যন্ত এক ছটাক কমেনি। সুযোগ হলে এখনও আমি দিনে অন্তত আধ-ঘণ্টা শোনার চেষ্টা করি। নতুন প্রতিভার সন্ধান পেলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি
মনোযোগী হই। তবে কোনও অনুষ্ঠানে শিল্পীকে বই বা খাতা সামনে রেখে গান গাইতে দেখলে এখনও আমার গা রি রি করে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের গান তো গায়ত্রী মন্ত্র একবার মুখস্থ হলে জীবনে আর ভুলতে নেই।
ঝাড়গ্রাম ছেড়ে আমরা মহানগরে চলে আসি কলকাতা একাত্তরের পয়লা জানুয়ারি তারিখে। ততদিনে আমাদের পরিচিত মা আর মা-তে নেই, শারীরিক-মানসিক নানা ব্যাধিতে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, একেবারে যেন অন্য মানুষ। সেই সব অসহনীয়, মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা এখানে টেনে আনা অবান্তর। প্রাসঙ্গিক যেটুকু তা হল, এত রোগ-ভোগও মায়ের রবীন্দ্র-প্রেমে এতটুকু রেখাপাত করতে পারেনি, রেডিও শোনার অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটা রেকর্ড প্লেয়ার যা আমি মায়ের কথা ভেবেই, বাবার নিঃশব্দ অসম্মতিকে অগ্রাহ্য করে কিনে এনেছিলাম। তখন রবি ঠাকুরের জন্মদিনে বড় মনোগ্রাহী একটা অনুষ্ঠান হত রবীন্দ্র-সদন প্রাঙ্গনে, কাক-ভোরে উঠে রেডি হয়ে প্রথম বাসটি ধরে সেখানে পৌঁছে সামনের দিকে মাটিতে বসে পড়াটা তখন ছিল আমাদের কয়েক বন্ধুর আবশ্যিক বার্ষিক কর্তব্য। রথ দেখার সঙ্গে কলাবেচাও হত। চারপাশে অনেক সুন্দরীরাও তো থাকত।
মা সাত-সকালের ওই অনুষ্ঠানে যেতে পারতেন না। কিন্তু তার পরের দিন বিকেল থেকে টানা পক্ষকাল রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে যে সব অনুষ্ঠান হত তার প্রত্যেকটিতে হাজির থাকতে না পারলে মনে হত যেন মায়ের জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। রোজকার টিকিট কাটার ক্ষমতা আমাদের ছিল না, অথচ মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আমার বড় কষ্ট হত। অচিরেই একজন মুশকিল আসানের সন্ধান পেয়ে গেলাম, নাম গোপাল ভৌমিক রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের তখন তিনি পদস্থ কর্তা। বাড়ি থেকে অদূরে সরকারি অফিসারদের কোয়ার্টারে থাকতেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার বেশ সুসম্পর্কই ছিল, নাম সব্যসাচী, ডেন্টাল কলেজে পড়ত। ওই গভর্নমেন্ট কোয়াটার্স তখন আমার ফি-বিকেলের আড্ডাস্থল, সেখানকার ছেলেদের সঙ্গেই মারতাম গুলতানি। একদিন আড্ডার মধ্যে রবীন্দ্রপক্ষের প্রসঙ্গ উঠলে আমি মায়ের দুঃখের কথাটা সবাইকে শোনালাম। শুনেই সব্যসাচীদা বলে উঠল, এটা কোনও সমস্যাই নয়। বাবা প্রতিদিন দুটো গেস্ট কার্ড পায়, আমাদের বাড়ি থেকে কেউ কখনও যায় না, তুই চাইলে রোজ সকালে এসে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারিস। আমার মনে হল যেন লটারিতে প্রথম পুরস্কারটা জিতে গিয়েছি। পরের দিন মাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম আমি-ই। একেবারে দ্বিতীয় সারির মাঝখানের দুটি আসন, যার চেয়ে ভাল জায়গা আর কিছু হতে পারে না। সেখানে বসে গান শুনতে শুনতে আমি ফাঁকে ফাঁকে মায়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আনন্দে চোখের কোনে জল চলে এসেছিল। আমার পক্ষে প্রতিদিন মাকে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব হত না, বিশেষ করে নৃত্যনাট্যগুলো অসহ্য লাগত, তবু মাকে দমানো যেত না। অশক্ত শরীর নিয়ে মা ৪১ নম্বর বাসে করে একাই যেতেন আর ফিরতেন। অনেক অল্প বয়সে মা’কে হারিয়েছি আমি, তবে তাঁর মতো রবীন্দ্রসঙ্গীত পাগল দ্বিতীয় কোনও মানুষের সন্ধান আমি আর পাইনি। সগ্গে বসে কবির জন্মদিনে মা নিশ্চয়ই তাঁকে গান শোনাচ্ছেন প্রাণ খুলে। ‘ও গো আমার প্রাণের ঠাকুর’।


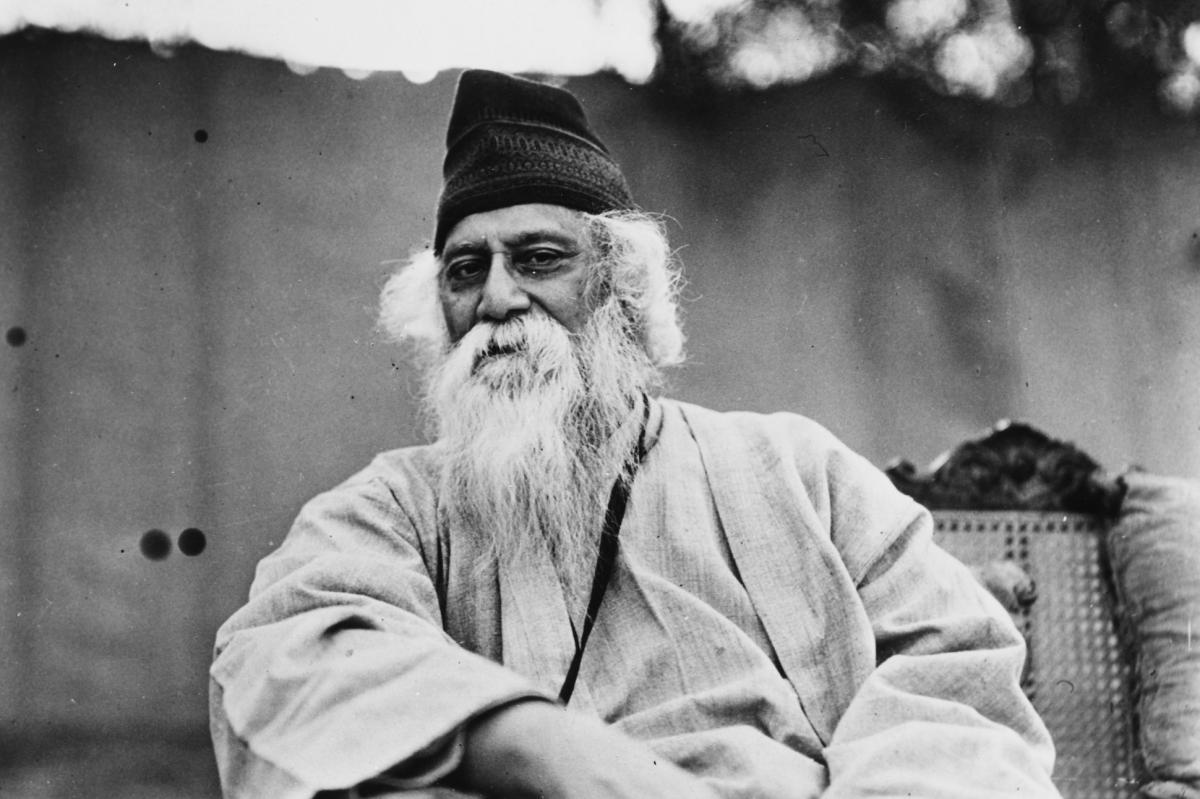

 Arts and Literature
Arts and Literature Bioscope
Bioscope Columns
Columns Green Field
Green Field Health World
Health World Interviews
Interviews Investigation
Investigation Live Life King Size
Live Life King Size Man-Woman
Man-Woman Memoir
Memoir Mind Matters
Mind Matters News
News No Harm Knowing
No Harm Knowing Personal History
Personal History Real Simple
Real Simple Save to Live
Save to Live Suman Nama
Suman Nama Today in History
Today in History Translation
Translation Trivia
Trivia Who Why What How
Who Why What How