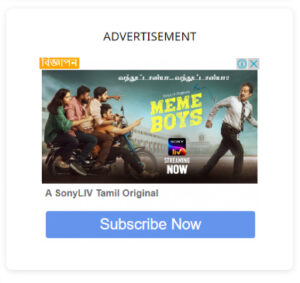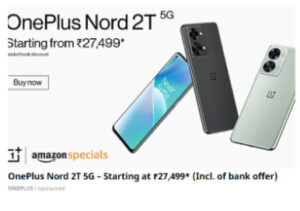- August 12th, 2022
হিম্মত এ মর্দা, মদদ এ খুদা
নিরানন্দর জার্নাল (৯)
হিম্মত এ মর্দা, মদদ এ খুদা
সুমন চট্টোপাধ্যায়
আরও অনেক কিছুর সঙ্গে হোয়াটস অ্যাপ একটি অতি জরুরি কাজ করে থাকে। ভুলতে না দেওয়া। এই যে গতকাল অক্ষয় তৃতীয়া ছিল, আমার তা মনেই ছিল না, কয়েক জন বন্ধুর মেসেজ মনে করিয়ে দিল।
আমার জীবনে এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিটির গুরুত্বও অক্ষয়। ২০০৯ সালের এই দিনে আমাদের ‘একদিন’ সংবাদপত্র পুনরায় প্রকাশ পাওয়া শুরু করেছিল। সে বছর অক্ষয় তৃতীয়া পড়েছিল এপ্রিল মাসে। সেই ঝঞ্ঝাবহুল যাত্রার রোমাঞ্চকর কাহিনি পরে হয়তো কোনও সময় বিস্তারিতে লিখব। আজ স্রেফ গৌরচন্দ্রিকা, যার মধ্যমণি আমার দীর্ঘদিনের সুহৃদ, সাচ্চা শুভাকাঙ্খী হরিশ চোপড়া।
হরিশ সফল ব্যবসায়ী, খাতার কারবার, ওর ব্র্যান্ডের নাম পায়ওনিয়র। আইটিসি-র মতো প্রবল প্রতাপশালী বহুজাতিকও খাতার ব্যবসায় এসে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত হরিশকে তার দীর্ঘ দিনের এক নম্বর অবস্থান থেকে একচুলও নড়াতে পারেনি। খাতার ব্যবসায় পায়ওনিয়র সত্যিই পায়ওনিয়র, ব্যবসার কেতাবী ভাষায় যাকে বলে মার্কেট লিডার।
হরিশ আমার বন্ধু তো বটেই এক অতি-আকর্ষণীয় চরিত্র। ওরা আদতে পশ্চিম পাকিস্তানের লোক, দেশভাগের ফলে শরণার্থী, তারই ধাক্কায় কলকাতায় এসে আশ্রয় খোঁজা। হরিশের বাবাও ব্যবসায়ী ছিলেন, খাতার নয়। হরিশের জন্ম, লেখাপড়া, বেড়ে ওঠা সব কিছুই সাবেক উত্তর কলকাতার গর্ভগৃহে। ফলে হরিশ যখন বাংলা বলে কারও বোঝার উপায় নেই সে আদতে পাঞ্জাবী। বিয়েও করেছিল বঙ্গ-ললনাকে, অকালে, অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি দুনিয়াকে আলবিদা করে চলে গিয়েছেন। রেখে গিয়েছেন একমাত্র পুত্রকে, সে-ও আধা বাঙালি হওয়ার সুবাদে বাবার মতোই বাংলায় স্বচ্ছন্দ।
হরিশ প্রত্যহ ছয়-সাতটি খবরের কাগজ কেনে যার মধ্যে দু’-তিনটি বাংলা। ইস্কুলের পরিশ্রমী ছাত্রের মতো প্রতিটি কাগজের মাস্তুল থেকে প্রিন্টার্স লাইন ও খুঁটিয়ে পড়ে, কোনও কিছুই তার নজর এড়ায় না। আমার চার দশকের সাংবাদিক জীবনে হরিশের মতো নিমগ্ন সংবাদ পাঠক আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। একটা সময় রোজ সকালে ডজন খানেক ‘একদিন’ বগলদাবা করে, রুবির মোড় থেকে উল্টোডাঙার মাঝখানে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসে যত কর্তব্যরত ট্রাফিক কনস্টেবল আছেন, তাদের বিলি করতেন। আমি রসিকতা করে বলতাম একদিনের পুলিশ-হকার। একদিনের সম্পাদক ছিলাম আমি, স্থপতি ছিল হরিশ। ওর অকৃপণ সাহায্য, সস্নেহ প্রশ্রয়, উদারতা, মহানুভবতা ছাড়া একদিন পুনঃপ্রকাশই করত না।
চরিত্রের সম্পূর্ণ বৈপরীত্যই আমার আর হরিশের নিবিড় বন্ধুত্বের মূল কারণ। আমি যা যা নই, কোনও দিন হয়ে উঠতেও পারলাম না, হরিশের স্বভাব, চরিত্র, দিনযাপনে সে সবই প্রতিফলিত হত। সফল ব্যবসায়ী হয়েও ও ফুটুনির ধার ধারে না, একটি নয়া পয়সাও অযথা খরচ করে না, যে কোনও প্রকার আলোর ঝলকানি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। সল্টলেকে ওদের তিনতলা সুন্দর বাড়ি, হরিশ দোতলায়, সবচেয়ে ছোট্ট ঘরটিতে মাটিতে মাদুর পেতে বিনা বালিশে রাত্রি-যাপন করে। স্ত্রী চলে যাওয়ার পরে ষোলো আনা নিরামিষাসী হয়ে গিয়েছে, যৎসামান্য খাওয়া-দাওয়া নিয়ম করে, এক্কেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে। হরিশ চোপড়া আসলে গৃহী-সন্ন্যাসী।
ভোর চারটেয় হরিশ গাত্রোত্থান করে, ইদানীং শুনলাম আরও এক ঘণ্টা আগে উঠে পড়ে। কেন? না বানপ্রস্থে যাওয়ার বয়সে ওর আহ্লাদ হয়েছে সংস্কৃত শিখবে, মাস্টার রেখে শিখছে, রাত তিনটেয় উঠে সেই শিক্ষাই ঝালিয়ে নেওয়া। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নিজে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে পড়ে শরীর-চর্চায়, অন্তত ঘণ্টা-খানেক দৌড়। ঘামে ভিজে চলে আসে কারখানায়, ঝাড়-পোঁছের কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কি না তার তদারকি করতে। সেখানে বসেই সংবাদপত্র অধ্যয়ন শুরু, যা চলতে থাকে বাড়ি ফেরার পরেও। স্নান-টান সেরে হরিশ ফের কারখানায় আসে সাড়ে ১০টা নাগাদ, থাকে রাত ন’টা-সাড়ে ন’টা পর্যন্ত। কারখানায় হরিশের অফিস ঘরটি যেন দেশলাইয়ের বাক্স, নিরাভরণ, অনভ্যস্ত অতিথির ক্লস্ট্রোফোবিয়া হওয়াও অসম্ভব নয়। সারা দিন ধরে নানা ধরনের লোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসে, হরিশের আপ্যায়ন বলতে নোনতা কালো চা আর দুটো মেরি বিস্কুট। এমন নয় যে ইচ্ছে করলে হরিশ বড় কোনও জায়গায় বসতে পারে না, কিন্তু সে যাবে না। ছোট্ট এক চিলতে ঘরই ওর চোখে খাসা।
এমনতরো মানুষের দেব-দ্বিজে ভক্তি থাকবেই, হরিশেরও আছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু-সঙ্গে ও তৃপ্তি পায়, বরাহনগর মঠে সপ্তাহে একদিন ও প্রণাম করতে যাবেই। পুজোর ছুটি হলে হরিশ হরিদ্বারে চলে যায়, গঙ্গার পাড়ে সাবেক গ্রামের লোকেদের তৈরি করা গেস্ট হাউসে একা একা দিন দশেক কাটিয়ে আসে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রতি রবিবার সকালে হরিশ গঙ্গা-স্নানে যেত, সাঁতরে এপার-ওপার করতে। ফেরার পথে তার প্রথম গন্তব্য উত্তর কলকাতায় ওর পুরোনো পাড়া যেখানে অনেক বাচ্চা-কাচ্চা ওর জন্য অপেক্ষা করে থাকে। ওরা জানে হরিশকাকু সঙ্গে প্যাকেট নিয়ে আসবে, তাতে থাকবে একটা সিঙাড়া, দু’টো মিষ্টি, একটা কলা। হরিশের জীবনে এটাই বিনোদন, সিনেমা, থিয়েটার, রেস্তোরাঁ, সুরাপাত্র থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে।
হরিশ নিজের উদ্যোগে খুঁজে খুঁজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ২০০৬ সালের কোনও একটা সময়ে। কলকাতা টিভি-তে চাকরি খুইয়ে আমার তখন কর্মহীন দশা। এক বন্ধুর বসন্ত রায় রোডের অফিসে একটা চেয়ার-টেবিল নিয়ে আমি অলস সময় কাটাই। হঠাৎ একদিন দুপুরে হরিশ সেখানে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে সামনের চেয়ারটিতে বসে পড়ে। জানায়, ও নাকি দীর্ঘদিন যাবৎ আমার লেখার গুণগ্রাহী পাঠক, হঠাৎ আমাকে অদৃশ্য হতে দেখে, কিছুটা উৎকন্ঠায়, লোকের কাছে খোঁজ নিয়ে ঠিকানা বের করে ওই অফিসে এসে পৌঁছেছে। দুঃসময়ে পরিচিত, উপকৃত লোকেরাও খোঁজ নেবে না, এটাই সংসারের নিয়ম। সেখানে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতজন যদি স্বেচ্ছায় আমাকে খুঁজে বের করে পাশে থাকতে চায় তাকে কী বলা উচিত? যে বিশেষণই প্রয়োগ করি না কেন, তা কি এই মানুষটার ক্ষেত্রে যথাযথ হবে?
২০০৭-এর ২১ ফেব্রুয়ারি বসন্ত রায় রোডের ওই ফ্ল্যাট-বাড়িতেই একদিনের জন্ম হয়েছিল। নিজের ফ্ল্যাট ব্যাঙ্কে বাঁধা রেখে যে টাকা পেয়েছিলাম তাই দিয়েই যাত্রা শুরু হয়েছিল, কত ধানে কত চাল হয়, একটি খবরের কাগজ চালাতে কত অর্থ লাগে সে সব ব্যাপারে আমার জ্ঞান-গম্যিই ছিল না। ফলত, যেটা অনিবার্য ছিল, সেটাই হল। অর্থাভাবের কারণে কয়েক মাস পরে আমি একদিন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলাম। একটা স্বপ্নের অপমৃত্যু হল।
তবু স্বপ্নটা তুষের আগুন হয়ে মনের মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলতেই থাকল। ভাবলাম, আর একটি সুযোগ যদি পাই, অর্থের সংস্থান করতে পারি, একদিন আবার বের করব। আমি একে বাঙাল, তায় বেপরোয়া, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কোনও কাজ করা আমার ধাতেই নেই। বছর দু’য়েক বাদে তেমন একটা সুযোগ তৈরি হল, কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী অর্থ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন আর হরিশ গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে জোগাড় করে দিল মাথার ওপরের ছাদ।
৭৪ নম্বর বেলেঘাটা মেইন রোড আদতে একটি ক্ষুদ্র শিল্পের ছোট ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, সেখানেই হরিশের কারখানা। আরও কয়েকটি কারখানা এবং আড়ৎ আছে অযত্নে পড়ে থাকা ওই প্রাঙ্গণে। এবরো-খেবড়ো রাস্তা, বর্ষায় এক হাঁটু জল জমে যায়, রাতের ঘুটঘুট্টে অন্ধকারে মা মনসার বাহনের উপদ্রব। ষোলো আনা খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের কর্মস্থল, কোনওটা লেদ মেশিনের কারখানা, কোনওটা সুতোর, কোনওটা আবার আইসক্রিমের স্টোরেজ। জামা-জুতো পরা, সিগারেট ফোঁকা, কারণে-অকারণে ইংরেজি বলা ভদ্রলোকের বাচ্চারা এমন সাব-অল্টার্ন ল্যান্ডস্কেপে নেহাতই বেমানান।
হরিশের সৌজন্যে এমন অভাবিত পরিবেশেই তৈরি হল একদিনের নতুন অফিস। হরিশ ওই তল্লাটের সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা, দক্ষিণ কলকাতা নিবাসী বাড়িওয়ালার সঙ্গেও ওর মধুর সম্পর্ক। কমপ্লেক্সে একটি কারখানার শেড খালি হতেই হরিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটি ভাড়া করে নিল। একটি ভাঙাচোরা, পরিত্যক্ত কারখানা ধীরে ধীরে একটি অফিসের চেহারা নিল, কয়েক লাখ টাকা খরচ হল, সবটাই দিল হরিশ। অবশেষে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে ফিতে কেটে অফিসের দ্বারোদ্ঘাটন করল আমার দিদি। হরিশের ঠোঁটে পরিতৃপ্তির সেই উজ্জ্বল হাসি আমার মনে এখনও অক্ষয়, অ-মলিন।
গতকাল অনেক দিন পরে হরিশকে টেলিফোন করেছিলাম কুশল সংবাদ জানতে। শুনলাম করোনায় সব এলোমেলো হয়ে গিয়েছে ওর জীবনে। কারখানা বন্ধ, ব্যবসার অবস্থাও তথৈবচ, সে নিজেও ছেলে-বৌমার কড়া শাসনে অনেক দিন যাবৎ গৃহবন্দি। চারদিকের এত প্রতিকূলতা, এত বিপন্নতার মধ্যেও হরিশের গলায় বিষন্নতার লেশমাত্র নেই, তেজি ঘোড়ার মতো এখনও টগবগ করে ফুটছে। কথায় কথায় ওর প্রিয় উর্দু প্রবচন শুনিয়ে হরিশ আমাকেও চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা করল। বলল, ‘আসল কথাটা কী জানো?’
না, জানি না। কোনটা আসল কোনটা নকল বুঝতেই পারি না আজকাল।
‘হিম্মত এ মর্দা, মদদ এ খুদা।’


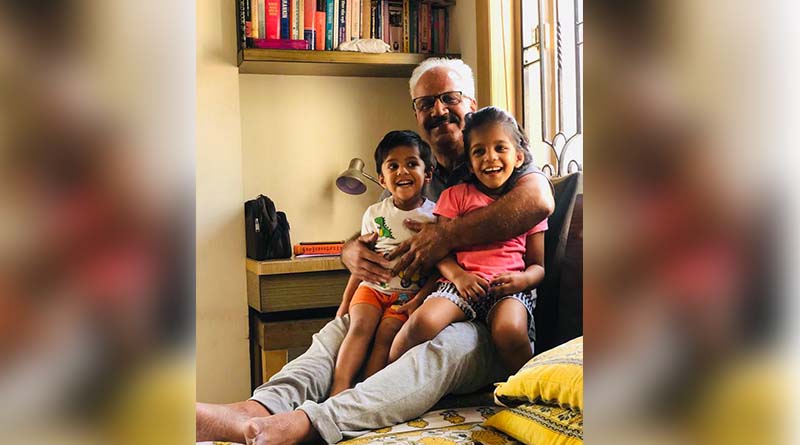

 Arts and Literature
Arts and Literature Bioscope
Bioscope Columns
Columns Green Field
Green Field Health World
Health World Interviews
Interviews Investigation
Investigation Live Life King Size
Live Life King Size Man-Woman
Man-Woman Memoir
Memoir Mind Matters
Mind Matters News
News No Harm Knowing
No Harm Knowing Personal History
Personal History Real Simple
Real Simple Save to Live
Save to Live Suman Nama
Suman Nama Today in History
Today in History Translation
Translation Trivia
Trivia Who Why What How
Who Why What How