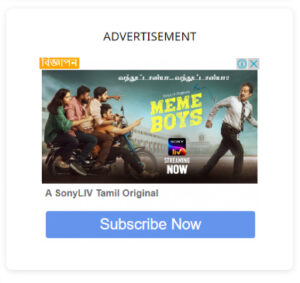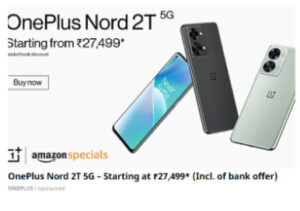- August 13th, 2022
পূর্ণকুম্ভ, শূন্য মন (চতুর্থ এবং শেষ পর্ব)
পূর্ণকুম্ভ, শূন্য মন
সুমন চট্টোপাধ্যায়
(চতুর্থ পর্ব)
তাহলে কি বত্রিশ বছর পরে কুম্ভে এসে রাস্তায় নামেননি কালকূট? আলবাত নেমেছিলেন। রোজ বিকেলে নিয়ম করে। সকালে লেখা। দুপুরে খাওয়ার পরে সামান্য বিশ্রাম, তার পরেই বেরিয়ে পড়া। গায়ে বাহারি পাঞ্জাবি-পাজামা, পায়ে দুধ-সাদা কোলাপুরি চপ্পল, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ, এক মাথা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, চঞ্চল চোখের চাহনিতে স্মিত হাসি। হোটেলের দরজায় দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া। ‘হল কী তোমাদের? কী হল, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও, বেরোতে হবে না?’ বেরোবার মতো সহজ কাজেও পরনির্ভরশীলতার জন্য ছটফট করতেন কালকূট। দেরি হলে আর রক্ষে নেই। শীর্ষেন্দুদা আর আমি, দু’জনেই সোজা বৌদির পিছনে।
হোটেল থেকে ব্রহ্মকুণ্ড, সোজা পথে গেলে বড়জোর মাইল খানেক। প্রথম দু’দিন গাড়ি যাওয়ার অনুমতি ছিল। তাও অর্ধেক রাস্তা। বাকিটা হণ্টন। হাঁটতে হাঁটতে কালকূট যখন তখন থমকে দাঁড়ান। যার তার সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করা করেন। ব্রহ্মকুণ্ডে নামার ঢালের মুখেই একটা সাইন বোর্ডে লেখা ‘জ্যোতিষী কা হাইকোর্ট’। ডেকে ডেকে দেখালেন আমাদের। এতই মজা পেয়েছিলেন যে পরের দিন লিখলেন, ‘জ্যোতিষী কা হাইকোর্ট। উঁহু কখনও দেখিনি, এমন কি সিটি বা জাজেস কোর্টও দেখিনি। দাঁড়িয়ে পড়তেই হল, তা দাঁড়ালেই বা, কে-ই বা তোমাকে দেখেছে। জ্যোতিষী কা জজ সাহেব? আমার মতো বিচারপ্রার্থীর জজিয়তি তিনি বোধহয় করেন না। আরও দু’পা এগোলে জ্যোতিষী কা সুপ্রিম কোর্টও পাব না তো?’
দু’পা এগোলেই হর-কি-পিয়ারি। ব্রহ্মকুণ্ড। সব পুণ্যার্থীর সুপ্রিম কোর্ট। পিয়ারি? না পৌরী? মানে কী? সিঁড়ি? না ঘাট? কৌতূহলী কালকূটের জিজ্ঞাসার আর শেষ নেই জেনো। চেহারা দেখে যাকেই কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানা বলে মনে হচ্ছে, ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে তাকেই প্রশ্ন করছেন, ও মহাশয়, বলতে পারেন পিয়ারি না পৌরী? সিঁড়ি না ঘাট? ঘাটের পুণ্যার্থীরা দিতে পারে না সদুত্তর।
তবে ঘুরে ফিরে ওই হর-কি-পিয়ারির ঘাটেই ফি-সন্ধে আসা চাই কালকূটের। পায়ে হাঁটার পথে চলা নিষেধ সেই ঘটিপূরণ ঘাটের ভিড়ে হারিয়ে গিয়ে রোজ মোটাসোটা দক্ষিণা দিয়ে একটা কাঠের বাক্স ভাড়া করতেন কালকূট। বাক্সের মালিকের কাজ ছিল স্নানার্থীদের জামাকাপড় রাখা আর তাদের স্নান সারা হলে কপালে রক্তচন্দনের তিলক এঁকে দেওয়া। রোজ পণ্ডিতজি তিলক আঁকতেন কালকূটের প্রশস্ত কপালে। পাছে আমরা ভাবি ধম্মে মতি হয়েছে কালকূটের, তাই কানে কানে ফিসফিস কর বলতেন, ‘এই জায়গাটা জয় করতে হল না! বুঝলে না, এটা তার স্বীকৃতি। জয়তিলক।’
ঘাটের উপর বসে থাকতে থাকতেই একদিন দেখা হয়ে গেল প্রণবানন্দজির সঙ্গে। তাঁর হাতের লাঠিটা ছিল দুধ-গোখরো সাপের গড়নের। দেখেই তাতে টান দিলেন কালকূট। ভেবেছিলাম এক প্রস্ত ঝগড়াঝাঁটি হয়ে যাবে বোধহয়। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, কালকূট তাঁর লাঠিটি স্পর্শ করায় কিঞ্চিৎ গর্বই যেন অনুভব করলেন গেরুয়াধারী স্বামীজি। তার পর একগাল হেসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, ‘সমরেশদা না? শরীর এত খারাপ হয়ে গেছে যে প্রথমে চিনতেই পারিনি। আমিও নৈহাটির ছেলে। একদিন হৃষিকেশে আমাদের আশ্রমে আসবেন।’ গিয়েছিলেন ফিরে আসার আগের দিন। গঙ্গার এপার পর্যন্ত। ঝোলা সেতু পেরিয়ে ওপারে যাবার শারীরিক ক্ষমতা তখন ছিল না কালকূটের।
গঙ্গার মূল ঘাটের চেয়েও কালকূটকে বেশি আকর্ষণ করত পাশের শীর্ণ নীল ধারা আর দূরের চণ্ডী দ্বীপ। বলতেন, আসল গঙ্গা তো ওই নীল ধারাই। এ তো শিবের জটার গঙ্গা নয়। মানুষের গঙ্গা। নীল ধারার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর মন তলিয়ে যেত সুদূর ইতিহাসের অতলে, ‘আমি আস্তিক নই, ধার্মিকও নই। কিন্তু যেখানেই ইতিহাসের সন্ধান পেয়েছি, মনের ভিতর নাড়া দিয়ে উঠেছে। ভাবতে পারো, এই সেই জায়গা যেখানে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে বিয়ে করার আগে, মাতা কুন্তীকে সঙ্গে নিয়ে এই নদীতট পর্যন্ত চলে এসেছিল। মহাবলী গন্ধর্বরাজ তখন অঙ্গনা-পরিবৃত হয়ে এখানে বিহার করেছিলেন। অর্জুনের উপস্থিতিতে বিরক্ত হয়ে তিনি যুদ্ধের আহ্বান করেন। গন্ধর্বরাজের চিত্ররথ জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু কেন আমি আজ গন্ধর্বরাজের লীলাভূমির সন্ধান করছি বলো তো?’
‘কেন?’
‘কেন না আমি যে অমৃতের সন্ধান করছি।’
শরীর বৈরী। সন্ধানের ইচ্ছে তবু যে কিছুতেই দমিত হয় না। অতএব রাত ঘন হলে চলো সাধুদের আখড়ায়। চলুন।
চৈত্র-অমাবস্যার দিন হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা সবাই নাগা সন্ন্যাসীদের স্নানযাত্রা দেখছি। বেজায় কড়া পুলিশি বন্দোবস্ত ছিল সারাদিন। উপরে দাঁড়াতে মানা, ছবি তুলতে মানা, সাধুদের দেখে হাসতে মানা। প্রয়াগের সঙ্গমে প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন নাগা বাবারা। অতএব কোনও ঝুঁকি নয়। নয় কোনও প্ররোচনাও।
কালকূটেরই শুধু কোনও ভয় নেই। সেদিন রাতেই জুমা আখড়ায় নাগা সন্ন্যাসীদের ডেরায় নিয়ে গেলেন শীর্ষেন্দুদা আর আমাকে। কালকূট আগে, পিছনে পিছনে আমরা দু’জন। আখড়ার মুখে সংকীর্ণ গলির পথটা অন্ধকার, পিচ্ছিল। পথ আগলে দাঁড়িয়ে বাসন ধুচ্ছিল কমবয়সী হাড়ে-হাভাতে চেহারার এক নাগা সন্ন্যাসী। বার কয়েক বলার পরেও রাস্তা দিচ্ছে না দেখে, হাতের টর্চের আগাটা দিয়ে সজোরে তার ঘাড়ে আঘাত করলেন কালকূট। ঘাবড়ে গিয়ে নাগা সরে গেল। এক্ষুনি একটা প্রলয় কাণ্ড বাধার আশঙ্কায় আমরা দু’জনে প্রমাদ গুনছি। কিন্তু কালকূট গট্ গট্ করে ঢুকে পড়লেন আখড়ায়। এমন ভাবে, যেন ওই আখড়ায় নগ্ন সাধুরা তাঁর কতদিনের পরিচিত। যার কাছে ইচ্ছে যাচ্ছেন, সাধুর মেজাজমর্জি বুঝে দক্ষিণা দিচ্ছেন আর খোশগল্প করছেন। চলতে চলতে এক সাধুবাবার পাশে বসে তার বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে গাঁজার কল্কেতে দিলেন সুখটান। তার পর ওই কল্কের আগুনের ফাঁক দিয়েই বাঁকা চোখে মিটি-মিটি চাইতে চাইতে বললেন, ‘বৌদিকে আবার বলে দিও না যেন। এটা হল সপ্তমীর দম। সাধুর গুরুভাষায় বিশুদ্ধ গঞ্জিকা।’ প্রয়াগের রাস্তায় দিদিমার পিছু ধরে আশ্রয়ের সন্ধানে যাওয়ার সময় ভাইপো পেল্লাদের মুখে গাঁজার নাম প্রথম শুনেছিলেন কালকূট। নিরম্বু উপবাসভঙ্গের জন্য, খুড়ির কাছে পয়সা চেয়েছিল পেল্লাদ। ওই পেল্লাদের কল্কেতেই কি প্রথম গঞ্জিকা সেবন করেছিলেন কালকূট? কে জানে। দুই অভিজ্ঞতায় পার্থক্য শুধু একটাই: প্রয়াগে নেশা করে চোখ রাঙানোর সময় বৌদির চোখ-রাঙানির পরোয়া করেননি কালকূট।
যেতে হয়েছিল আরও অনেক আখড়ায়। চণ্ডী দ্বীপের আধো আলো আধো অন্ধকার ছাউনির ভিতরে। যেতে পারেন ততটুকুই, যতটুকু শরীরে দেয়। কিন্তু তাও কি করার জো আছে? লোক ভরছে। মেলা জমছে। আর ততই বেড়ে চলেছে পরিচিত-অপরিচিত গুণমুগ্ধের সংখ্যা। রাস্তায় বেরোলেই কানে আসছে, ‘দ্যাখ দ্যাখ, সমরেশ বোস।’ তারপরেই অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে দেওয়া। সই সই সই। শেষ পর্যন্ত ভক্তদের ঢল নামতে শুরু করল হোটেলেও। কাক-ভোর থেকে মাঝরাত্রি। বালুরঘাট থেকে আসা একদল শিক্ষয়িত্রী তো কালকূটের সম্মানে তাঁদের হোটেলে একটা মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করলেন। বঙ্গললনারা তাঁকে এত খাতির যত্ন করেছিলেন, কিন্তু কালকূটের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন উত্তর ভারতীয় ললনারা। ‘ওরা সত্যিই উর্বশী।’
তফাত যে এখানেও। বত্রিশ বছর আগে প্রয়াগযাত্রার সময় কালকূটের ছিল ভরা যৌবন, ছিল না এত খ্যাতি। হরিদ্বারে শরীরের সঙ্গে জুড়েছে খ্যাতির বিড়ম্বনা। প্রথমবার অমৃত কুম্ভের সন্ধানে গিয়ে কালকূটের মাথায় উঠেছিল খ্যাতির শিরোপা। দ্বিতীয়বার তাঁর পায়ে সেই খ্যাতির বেড়ি। নিজের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা।
ব্যাপারটা যে কালকূট নিজেও বুঝতে পারছিলেন না এমন নয়। পূর্ণ কুম্ভের আগের দিন মাঝরাতে হোটেলের ঘরে ঘরে আমরা যখন ঘুমে বিভোর, কাউকে না জানিয়ে কালকূট বিছানা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন পান্থশালার পূবে রেল-স্টেশনে, যেখানে অহর্নিশি বাঁধ-ভাঙা ঢেউয়ের মতো ট্রেনের জনতা আছড়ে পড়ছিল। পরের দিন তাঁর মুখে যেন যুদ্ধজয়ের হাসি।
বৌদির ধমক খেয়েও, করুণ মুখ করে বললেন, ‘কী করব বলো, ইস্টিশনের বাঁশি আমায় ছেলেবেলা থেকেই টানে।’ ইস্টিশন টেনেছিল, না শ্যামা? বৃদ্ধ স্বামীর চিতা জ্বালিয়ে প্রয়াগ থেকে ফিরেছিল শ্যামা। কত আর বয়স তখন নতুন বিধবার। বড় জোর বাইশ-তেইশ। বত্রিশ বছর পরে শ্যামার বয়স হয়েছে তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন। আবার কি বিয়ে করেছে শ্যামা? নাকি প্রতীক্ষায় আছে সেই যুবকটির, যমুনা-তীরে দাঁড়িয়ে যাকে দেওয়ার জন্য লুলা বলরামের হাতে সে আঙুলের আঙটিটি খুলে দিয়েছিল? কালকূট ইস্টিশনে গিয়েছিলেন কি তারই খোঁজে? গিয়েছিলেন, কিন্তু খোঁজ পাননি। শ্যামার বদলে দেখেছিলেন এক পান-খেকো ভৈরবীকে।
সেই হতাশাতেই কি ডাক্তারের বেঁধে-দেওয়া কড়া নিয়ম চূড়ান্ত ভাবে ভেঙে ফিরে আসার আগের দিন হর-কি-পিয়ারির ব্রহ্মকুণ্ডে, প্রায় উলঙ্গ হয়ে স্বচ্ছসলিলা হিমশীতল জলে ডুব দিলেন কালকূট? ‘লজ্জা কী? নগ্নতাই এখানে সকলের ভূষণ।’ ডুব দিয়ে কী প্রার্থনা জানাবেন গঙ্গা মাইয়ার কাছে? ‘বলব, অমৃতে আমাকে নিয়ে চলো। সেই নিজের আর্তির মধ্যেই এই লক্ষ রূপের অনুপুঙ্খে যাব। বলব, অমৃতং গময়ঃ।’ সকলের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও টুনি বৌদি গঙ্গায় নামলেন না। ‘নামব। সেদিন, যেদিন তোর দাদা জ্ঞানপীঠ পাবে।’
ন’দিন একটানা অষ্টপ্রহর কাটিয়ে দিল্লিতে ফিরে এসে তাঁর দ্বিতীয় অমৃতযাত্রার অভিজ্ঞতা সম্বলিত পাণ্ডুলিপিটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন কালকূট। বলেছিলেন, সময়-সুযোগ পেলে আরও পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা লিখবেন। আর যাওয়ার আগে সেই পরিচিত হাসি-মাখা মুখে বলে গিয়েছিলেন, ‘রিপোর্টারির চাকরিটা খারাপ লাগল না। অভীককে বলব, তোমাকে আর আমাকে আবার যেন এক সঙ্গে প্রয়াগে পাঠায়।’
বছর পেরোলেই প্রয়াগে আবার কুম্ভ। সঙ্গমে কোটালের বানে ধরো যদি শ্যামার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সে যদি তোমার খোঁজ করে, কী বলব?
বলব, অমৃতের সন্ধান তোমাদের কালকূট পেয়ে গেছে গো! (শেষ)



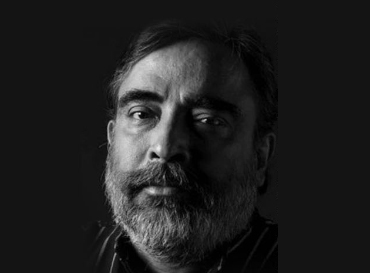
 Arts and Literature
Arts and Literature Bioscope
Bioscope Columns
Columns Green Field
Green Field Health World
Health World Interviews
Interviews Investigation
Investigation Live Life King Size
Live Life King Size Man-Woman
Man-Woman Memoir
Memoir Mind Matters
Mind Matters News
News No Harm Knowing
No Harm Knowing Personal History
Personal History Real Simple
Real Simple Save to Live
Save to Live Suman Nama
Suman Nama Today in History
Today in History Translation
Translation Trivia
Trivia Who Why What How
Who Why What How