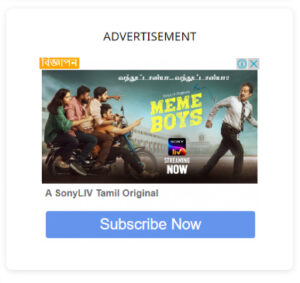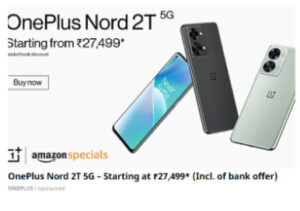- August 13th, 2022
আমার নাই বা হল পারে যাওয়া
জ্যোতির্ময় দত্ত
আমার নাই বা হল পারে যাওয়া (প্রথম খণ্ড)
সুমন চট্টোপাধ্যায়
তাঁর রামধনু-রঙা, বহুমাত্রিক, অবিশ্বাস্য জীবনচরিতের তল না পেয়ে কিঞ্চিত বিভ্রান্ত আমার প্রয়াত পিতৃদেব একবার সকৌতুকে জ্যোতির্ময় দত্তকে জিজ্ঞেস করে বসেছিলেন, ‘আপনার পূর্বপুরুষ কি ডাকাত ছিলেন?’
জ.দ জবাবে কী বলেছিলেন, সাড়ে তিন দশক পার করে এখন আর তা মনে করতে পারছি না। তবে হঠাৎ মনে হল আমাদের দু’কামরার বিবর্ণ আটপৌরে ফ্ল্যাটবাড়ির বসার ঘরে যেন নায়াগ্রা জলপ্রপাতের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ডাকাত ছাড়া কার সাধ্য এমন অনাবিল, উচ্চনাদ, আকাশ-ছোঁয়া অট্টহাসি হাসতে পারেন?
ছিঁচকাঁদুনে, পেটরোগা, ভীতু ভাঙালি বড় জোর স্বভাব দোষে ছিঁচকে চোর হতে পারে, ‘ডাকাত’ হওয়া তার পক্ষে ততটাই অসম্ভব যতটা হরিয়ানার জাঠের বেটার পক্ষে কবিতা লেখা। ‘ডাকাত’ হতে হলে কলজেতে লাগে দুর্জয় সাহস, অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে নিকশ কালো অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে পারার দুর্দমনীয় আকাঙ্খা। কিন্তু কোন ভগীরথের জটা হতে পারে এমন অবাঙালিচিত, রোমান গ্ল্যাডিয়েটর সদৃশ বীরত্বের উৎসস্থল? জ.দ নিজেই সেই রহস্যের কিছুটা কিনারা করে দিয়ে যা বলেছেন তা থেকে পরিষ্কার, আমার পিতৃদেবের আল-টপকা প্রশ্নটি সেদিন সঠিক দিশাতেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। কী আশ্চর্য, জবাব আছে তাঁর ধমনীর রক্তে, আধুনিক বিজ্ঞান যার নাম দিয়েছে ‘জিন’।
জ.দ-র বাবা ভোলানাথ দত্ত খুলনার যে গ্রামে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন কোনও দৈব-বশে তার নাম ছিল ‘সাহস’!। পিতার রক্ত পুত্রকে পুষ্ট করবে প্রকৃতির এই নিয়ম যতটা স্বাভাবিক, সর্বজনগ্রাহ্য, গ্রামবাসীকে তাঁর ভিটেমাটির নামের সার্থকতা বহন করতে হবে এই ঘটনা ততটাই অলৌকিক এবং কাকতালীয়। অথচ রুদ্র ভোলানাথের জীবনে ঠিক সেটাই হয়েছিল। তিনি গতরে ছিলেন সাক্ষাৎ হারকিউলিস, মেজাজে জেদি, এক রোখা, স্বাবলম্বী, আনখশির সৎ। তিনি জামা-কাপড় ছাড়ার মতো সহজে চাকরি ছাড়তে পারতেন, আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করতেন তেমন দুর্দিন এলে হাওড়া কিংবা শিয়ালদায় কুলিগিরি করে তাঁর পারিবারিক ফুটবল টিমের (স্ত্রী ও দশটি সন্তান) ভরণ-পোষণ করতে পারবেন। মৃত্যুকে তিনি এক রকম ডেকেই এনেছিলেন লা-পরোয়া মনোভাব নিয়েই।
‘বাপ কা বেটা সিপাহি কা ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়াথোড়া’ হবেই। জ.দ-র অর্ধেক জীবনের (১৯৩৬-১৯৭৬, মানে প্রথম চল্লিশ বছরের) এই অতীব সুখপাঠ্য, রোমাঞ্চকর, প্রায় স্বর্গীয় আলেখ্যর ছত্রে-ছত্রে রয়েছে এমন এক জীবনের বর্ণনা, গল্প, উপন্যাস, সিনেমাতেও যার দেখা মিলবে না, বাস্তব বলে মেনে নেওয়া তো দূরস্থান! এক জীবনে কত রকমের কাজই না একজন মানুষ করেছেন বা করতে পারেন! কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রিটে কর্মজীবনের গোড়ায় ছিলেন আপার ডিভিশন ক্লার্ক, তারপর আমেরিকার রেস্তোঁরায় পিৎজা কারিগর, ডিশ ওয়াশার, শিকাগো এবং আয়োয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-অধ্যাপক। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, তিনি সর্বত্রগামী, জানেন নৌ কিংবা অশ্ব-চালনা এবং গ্লাইডিং। কোনওটাই স্রেফ শখের মজদুরি নয়, জীবন পণ করে শেখা। হাতের কাঠের কাজে এমন উদ্ভাবনী ছটা যা দেখে নিপুণ ছুতোরও লজ্জা পেতে পারে বৈ কী। ছবি আঁকতে পারেন, ইচ্ছে করলে হতে পারতেন ভাস্করও। পেশা সূত্রে জ.দ-র পরিচয় সাংবাদিকের, সেখানেও তিনি সব্যসাচী, প্রায় বিলুপ্ত প্রজাতি দ্বিভাষিক বাঙালির সফল, সার্থক প্রতিনিধি। নিজেই লিখেছেন, ইংরেজি তাঁর জীবিকা, বাংলা জীবন। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে একদা শহর-মাতানো ‘কলকাতা’ পত্রিকা বের করেছিলেন, জনক ছিলেন কলকাতার ময়দানে স্বপ্লায়ু মুক্তমেলার। বঙ্গোপসাগরের মোহনার কাছে গাঙড়ার চরে আবিষ্কার করেছিলেন পয়লা নম্বর গ্রাম, সেখানে মাটির নীড় বেঁধেছিলেন দু’দণ্ড শান্তির আশায়। সেই গাঁ-ই ছিল জ.দ-র জীবনের বনলতা সেন। জ.দ-র কথায়, ‘জীবনের বত্রিশ ব্যঞ্জন ভোজে, প্রত্যেক পাত্রেরই করেছি আস্বাদন।’
ছপ্পর খুলে এত দেওয়ার পরে ঈশ্বর জ.দ-কে কেবল একটি গুণে বঞ্চিত রেখেছেন। ছন্দে তিনি ডি লিট পাওয়ার অধিকারী, সুরের ক্ষেত্রে ভূতের বর পাওয়ার আগেকার গুপি গাইন। একবার শান্তিনিকেতনে প্রতিভা বসুর বাড়ির বাগানে পবন দাস বাউলের গলায় গলা মেলানোর চেষ্টা করেছিলেন। রে রে করে উঠেছিলেন তাঁর শ্বশ্রুমাতা, ‘বন্ধ কর, বন্ধ কর, এ গান শুনলে বাচ্চু (নীলিমা সেন, প্র.ব-র প্রতিবেশী) নির্ঘাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়বে।’ পবন ধমকে বলেছিলেন, ‘খবর্দার আপনি তালও দেবেন না!’
জীবন নিয়ে এমনতরো বিবিধ পরীক্ষা করতে সাহস তো লাগেই। তবে সেটাই কি হতে পারে একমাত্র চালিকাশক্তি? আর পাঁচজনে জীবনের যে সময়টায় ধাপে ধাপে কেরিয়ার গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়, সেটাই যেখানে সংসারের প্রায় অভ্রান্ত নিয়ম, সেখানে আর একজন, যিনি সর্বার্থে শিক্ষিত, একগুলি কাজে পারদর্শী, জাগতিক প্রাপ্তির কোনও আশা না করে, দারা-পুত্র-পরিবারকে সমূহ বিপন্নতার মধ্যে ফেলে দিয়ে, স্বজন-বান্ধবদের দূরে ঠেলে দিয়ে, এমন স্বেচ্ছাচারী-ইউটোপিয়ান হয়ে ওঠেন কীসের তাগিদে? সম্ভাব্য উত্তর, একমাত্র তিনি যদি ‘জিনিয়াস’ হন। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, নিয়ম, নিরাপত্তা, ইত্যাদিজাগতিক প্রাপ্তির মোহ ভুলতে পারেন কেবল ‘জিনিয়াস’রাই। সময় বা স্থান তাঁদের পায়ের নীচে দলিত হয়, তাঁদের জীবন হয়ে ওঠে ‘পিরিয়ড পিস’-এর ঠিক বিপরীত। জ.দ নিজ মুখে অবশ্যই এ কথা লেখেননি, সেটা প্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু কোনও স্থায়ী গন্তব্য স্থির না করে, কেবলই গতির আনন্দে ভাঙা-গড়া, চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে দিয়ে জীবনকে নিয়ে যাওয়ার কাহিনীর উপসংহারে ভিন্ন সংজ্ঞা নিরুপণ অসম্ভব। ওই অস্কার ওয়াইল্ড যেমন বলেছিলেন, ‘জিনিয়াস ইজ বর্ন, নট পেইড।’
জ্যোতিষ-শাস্ত্রে না থাকলে থাকুক, অনিবার্য ভাবে জ.দ-র জন্ম হয়েছিল ‘কবিতা’ লগ্নে। কাব্যেই সমর্পিত তাঁর জীবন, হীরক-দ্যুতির বাংলা গদ্যও যেন কবিতার ছন্দেই লেখা। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর বিষয় ছিল ইংরেজি সাহিত্য, তার অনেক আগে থেকে, বস্তুত আ-শৈশব তিনি গ্রন্থ-কীট। শেক্সপিয়র বা মিল্টনের ভাষার উচ্চারণ রীতিতে জ.দ অভ্যস্ত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় বা রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠের সন্ধান পাওয়ার আগেই। সেই সাহিত্য-প্রেমী মন কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই মিশেছিল যে মোহনায় তার নাম বুদ্ধদেব বসু ওরফে বু.ব, যিনি অচিরেই তাঁর শ্বশুরমশাইও হয়ে উঠেছিলেন। জ.দ-র কথায়, তাঁর বাবা ছিলেন শরীরের জনক, মনের জনক বু.ব। কবিতা লিখে বু.ব-র মন জয় করার পরেই তাঁর কন্যা মীনাক্ষীর পানি গ্রহণের পথ প্রশস্ত হয়েছিল, আরও অনেক ব্যর্থ প্রেমিককে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে। কবিতা ভবনের সেই স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনবেশী জ.দ-র মীনের আঁখি বিদ্ধ করার মধুর প্রমের কাহিনি আগাপাশতলা মজার।
সেই বিয়েতে আচার-অনুষ্ঠান হয়নি। যোগেশচন্দ্র বাগল সংস্কৃত মন্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন, সাক্ষী ছিলেন নরেশ গুহ ও অশোক মিত্র (জ.দ যাঁকে বলেছেন রুক্ষ অর্থনীতিবিদের মোড়কে বিশুদ্ধ কবি) আর গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন রাজেশ্বরী দত্ত। পরে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর ভোজ সভায় তাঁর টেবিলে ছানার পায়েস না আসায় গভীর মনস্তাপ হয়েছিল শিবরাম চক্রবর্তীর। ওয়েটারকে ডেকে তিনি চাইতে পারতেন, টেবিলে একই সঙ্গে বসা ভোলানাথ দত্ত তা হতে দেননি। ক্রুদ্ধ শিবরাম জ.দ-র পিতাকে দিন কতক পরেই উপহার দিয়েছিলেন তাঁর লেখা ‘স্বামী কেন আসামী!’
‘আমার নাই বা হল পারে যাওয়া’ একটি ‘সকল কলুষ তামস হর’ আত্মচরিত, গ্রন্থের শেষে নির্ঘণ্টে চোখ বোলালে অমনযোগী পাঠকও টের পেয়ে যাবেন বাঙালির শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-বিজ্ঞান-মনীষার জগতের সবচেয়ে আলোচিত, উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের সমাবেশ ঘটেছে এখানে। ফলে বইটির নাম হতেই পারত ‘নক্ষত্রেরা আসে দলে দলে।’ এখানে কেবলই উদ্ভাসিত আলোর ছটা, অন্ধকারের লেশটুকু পর্যন্ত নেই, তাঁদের প্রতি লেখকের দৃষ্টি এক চক্ষু হরিণ সুলভ, সবাই ভালো, সবাই মহান, সবাই প্রতিভাবান। জবানবন্দিতে জ.দ-র কৈফিয়ৎ, ‘এই বৃত্তান্তে আমার স্বভাবসুলভ জটিলতা, বিশ্লেষণ, কুটতা কিছুই নেই। আমি শুধু চেষ্টা করেছি একটা নিরপেক্ষ, ব্যক্তিগত রোষ-কি-অসূয়াহীন ধারাবাহিক বর্ণনা দিতে।’ লেখকের সচেতন সিদ্ধান্ত, কারও কিছু বলার থাকতে পারে না, টেক ইট অর লিভ ইট। এখানে কেবল পরমান্ন পরিবেশিত হয়েছে যার সুগন্ধে মাতোয়ারা লাগলেও অতি-মিষ্টত্বের কারণে কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ গা-গোলানো ভাবও ওঠে। মনে প্রশ্ন জাগে ভগবান কি তাহলে সত্যিই বৃদ্ধ হলেন?
এক নিঃশ্বাসে বইটি ফেলার পরে আমার বুকটা ভারী হয়ে ওঠে, প্যারাডাইস লস্ট-এর বেদনায়। বিস্ময়ের ঘোর কাটার পরে চোখ কচলে ভাবতে বসি পাঁচ-ছয়-সাতের দশকে কলকাতা তাহলে সত্যি প্রাচ্যের পারী-ই ছিল? ‘বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ মা যে সময় সত্যিই ‘অপরূপ রূপে বাহির’ হয়েছিলেন, এই জীবনালেখ্য তার প্রাণবন্ত, প্রামান্য, বহুবর্ণে রঞ্জিত দস্তাবেজ। মায়ের যে ‘মূরতি’ দেখে আমাদের যাদের অষ্টপ্রহর হাহুতাশ হয়, স্বর্গভ্রষ্ট জীবনটাকে কেবলই আত্মগ্লানিময় মনে হয়, এই বই সেখানে মনোরম মনের মলমের কাজ করে, আশা জাগে বাংলার আকাশে এমন অমানিশা স্থায়ী নাও হতে পারে, আবার হয়তো আলো ফোটাতে পারে নতুন এক ঝাঁক নক্ষত্র-রাশি। জানতে ইচ্ছে করে প্রেম আর বন্ধুত্বের দুই রণ-পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে যে জ্যোতির্ময় দত্ত সদর্পে বিরাশিতে নট আউট রয়েছেন, তিনিও কি আর এমন স্বপ্ন দেখেন? ‘চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি’, এটাই যদি জীবন আর অস্তিত্বের মর্মবাণী হয়, তাহলে নিরাশই বা হব কেন?
ফেরা যাক সে কালের কলকাতায়, যার অনুপম পটচিত্র জ.দ এঁকেছেন কলমকে তুলি বানিয়ে, ইতি-উতি হাস্যরসে চুবিয়ে। সেই কলকাতায় দক্ষিণের রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ছিল সাক্ষাৎ ‘কবি-টোলা’, বিষ্ণু দে, নরেশ গুহ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, এমনকী জীবনানন্দের শেষ জীবনের ভাড়া বাড়িটি, সবটাই ছিল পরস্পরের ঢিল ছোড়া দূরত্বে। ‘সবাই হাঁটা পথের মধ্যে। আলোচনা-অনুকরণ-বিতর্ক। দেড় মাইলও হবে না, পুরো রাস্তা আধুনিক বাংলা কবিতার এক মহাব্যস্ত কারখানা।’ যাদবপুরে সবে খুলেছে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিভাগ, বু.ব-র উদ্যোগে, সেখানে পড়াতে এসেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি স্টেটসম্যানের মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন অন্য কোনও কারণে নয়, কাগজটির ভাষা ধীরে ধীরে তাঁর কাছে ক্লান্তিকর মনে হয়েছিল বলে। কবিতার জগতেও তিনি ছিলেন স্বভাব-কবির অ্যান্টিথিসিস। পাঁচের দশকে তাঁদের গোড়ার দিকের ছাত্ররা ছিলেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় দেব, নবনীতা দেব (পদবীতে ‘সেন’ জোড়া হতে তখনও কিছুকাল বাকি)।
রাসবিহারী যদি ‘কবি-টোলা’ হয়, উত্তর কলকাতা তাহলে ‘গ্লোব নার্সারি’। সেখানে একদা রামমোহন-বিদ্যাসাগরের বাস ছিল ‘পরস্পরের অট্টহাস্যধ্বনি শ্রবণসীমার মধ্যে’। জ.দ লিখছেন, একশ বছর পরে সেখানে, বিশেষ করে শ্যামবাজার-শোভাবাজার অঞ্চলে ‘জ্বলে উঠেছিল সাহিত্য ও শিল্পের রংমশাল’। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ, অম্লান দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, শিবনারায়ণ রায় এবং গণেশ পাইন, মুখের সেই মিছিলে এ বলে আমায় দ্যাখ, তো সে বলে আমায়। প্রতিভা থাকলে, জীর্ণতম দেওয়ালেও চারা গজিয়ে ওঠে, জ.দ সেটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন সুনীল আর গণেশ পাইনের প্রথম জীবনের সংগ্রামের কাহিনি প্রত্যক্ষ করে। কঠিন কঠোর বাস্তবের সঙ্গে যুঝেও একজনের কলম থেকে যদি একটির পর একটি মুক্ত ঝরে থাকে তাহলে অন্যজন অর্জন করেছিলেন অনায়াসে রূপকথার জগতে চলে যাওয়ার ক্ষমতা।
ডিহি শ্রীরামপুর লেনে ছিলেন যামিনী রায়, যাঁর সংস্পর্শ লেখলের কাছে ‘দৈব উপস্থিতি’-র মতো লাগত। ‘টুকটুকে লাল মেঝেতে বসার প্রথা, আসবাব বলতে ছোট ছোট নিচু চৌকি, পাটিতে বসে উপুড় হয়ে’ তাঁর পট আঁকা। পার্ল রোডে আস্তানা ছিল আবু সয়ীদ আইয়ুবের যিনি ‘রূপে ছিলেন মুখল রাজকুমার, মেধায় ছিলেন বেনেদেত্তো কোচে কিংবা আর্তেজা ই গ্যাসের সমমানের দার্শনিক।’ তাঁকে দেখলে ‘মনে হত যেন সূর্যের খরতাপের বাইরে কোনও বিরল অর্কিড’। পাশাপাশি চলত প্রায় সব ঠিকানাতেই সান্ধ্য আড্ডা। কবিতা ভবনের আড্ডায় যদি বিজ্ঞানী সত্যেন বসু উপস্থিত, অন্য কোথাও পানের ডিবে হাতে পাহাড়ি সান্যাল, কোথাও রঘুনাথ গোস্বামী, কোথাও বিনয় মজুমদার, দীপক মজুমদার কিংবা টালমাটাল শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সেই কলকাতায় সারা বছর ধরে যাতায়াত ছিল প্রতীচ্যের দিকপাল পণ্ডিত, কবি, লেখক, বাউন্ডুলেদের। আসতেন অ্যালেন গিনসবার্গ, এডওয়ার্ড ডিমক, ক্লিন্টন সিলি, আর্থার কোয়েসলার। তর্কের পাঞ্জায় সবার সঙ্গেই হাজির জ.দ।
প্রেসিডেন্সি কলেজে জ.দ-রা ছিলেন ১৯৫১ সালের ব্যাচ। তাঁরা এতই প্রতিভাধর যে চারপাশে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র বসু, পি সি রায়, স্যার অশুতোষের স্মৃতিস্তম্ভগুলি তাঁর খেয়াল করেই উঠতে পারেননি। তাঁদের মাস্টারমশাইরাও বলতেন, একসঙ্গে এতজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র তাঁরা বহু বছর পাননি- পার্থসারথি গুপ্ত, সুবীর রায়চৌধুরী, বরুণ দে, সুখময় চক্রবর্তী এবং অমর্ত্য সেন। ছাত্র অমর্ত্য ছিলেন কেমন? ‘ছিপছিপে চেহারা, মালকোঁচা মারা ধুতির ওপর হাত গোটানো শার্ট, লালচে ফ্রেমের চশমা, হাতে ওয়েস্টমিনিস্টার স্টাইলের পাকানো ছাতা। কখনও আমাদের মতো তার বগলে বই দেখিনি। সে যে কখন পড়ত সেটাই ছিল একটা বিস্ময়।’ আরও একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল ছাত্র অমর্ত্যর। মেয়েদের কমন রুমের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের সঙ্গে অনর্গল আড্ডা মেরে যাওয়া।
সেদিনের কলকাতায় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর কফি হাউসে ‘হাউস অব লর্ডস ছিল, সেখানে একটা টেবিলে পেয়ালায় তুফান তুলে আড্ডা দিতেন শাঁটুল গুপ্ত, সুভাষ ঘোষাল, কমল কুমার মজুমদার, সত্যজিৎ রায়। অদূরে স্টেটসম্যান সবে ইংরেজদের হাত থেকে টাটাদের হাতে গিয়েও তার খবরের নির্ভরযোগ্যতা, আভিজাত্য, ইংরেজি মান সম্পর্কে সমান সচেতন। জ.দ এখানেই কাজ করেছেন ইংরেজ সম্পাদকদের সঙ্গে, এখানেই দেখেছেন সমর সেন, নিরঞ্জন মজুমদারকে যিনি অফিসের চেয়ে অ্যাম্বারে পানীয়ের টেবিলে বসেই সময় কাটাতে বেশি ভালোবাসতেন। এখানেই জীবন্ত কিংবদন্তী হামদি বে-র সঙ্গে তাঁর আলাপ, পরে ঘনিষ্ঠতা, তারও পরে একই ছাদের তলায় টানা পনেরো বছর বসবাস। ইংরেজি চর্চার আরও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন পুরুষোত্তম লাল, তাঁর রাইটার্স ওয়ার্কশপের মাধ্যমে। সেটা ছিল ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষায় কাব্য করার ঠেক। লেখক ঠিকই লিখেছেন, কলকাতা তখন ছিল সর্বার্থেই দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী। বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবী বলতে যা বোঝায়-অর্থাৎ নিস্পৃহ মননের চর্চা, তাদের দেখা মিলত এখানেই। সেই বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন সব নিয়মের বাইরে, স্বতন্ত্র, স্বাধীন। এমতো মননের চর্চার অনুকূল পরিবেশ ছিল গোটা দেশের মধ্যে একমাত্র এই কলকাতাতেই। তাঁদের বেশিরভাগই ইংরেজির ধার ধারেননি, বাংলা ভাষা দিয়েই বঙ্গ-ভাণ্ডারের বিবিধ রতন তাঁরা আবিষ্কার করে গিয়েছেন। এমন একটা কলকাতায় বড় হয়ে ওঠাই তো রীতিমতো ভাগ্যের বিষয়।
একটি জরুরি কথা বলা বাকি থেকে গেল। আমি যে জ.দ-কে চিনি তাঁর আত্মজীবনী লেখার কথা নয় একেবারেই। কেননা আত্মকথাকারের কারবার থাকে হয় ডন কিহোতো অথবা শাঙ্কো পাঞ্জাকে নিয়ে, নয়তো বা দুটোই। জ.দ-র চরিত্রে ‘হানড্রেড শেডস অব গ্রে’ থাকতে পারে, কিন্তু এই দুই গল্পের চরিত্রের ছায়া মাত্র নেই। না তিনি নিজেকে নিয়ে কখনও ভেবেছেন, না আছে তাঁর উগ্র অহংবোধ। তাহলে জ.দ এমন একটি স্বভাব-বিরোধী কাজ করে বসলেন কী করে? জবানবন্দিতে প্রেমিক লেখকের সরল স্বীকারোক্তি, বাষট্টি বছরের সহযোদ্ধা-সহধর্মিনীর প্ররোচনা তিনি চেষ্টা করেও এড়াতে পারেননি। পারবেনই বা কী করে? ‘আমাকে যে বাঁধবে ধরে সেই হবে যার সাধন’, সেই অসাধ্য সাধনের নায়িকা তো বরাবরই মীনাক্ষী দত্ত, জ.দ-র ঘূর্ণায়মান জীবনের একমাত্র বিশ্বস্ত, সর্বংসহা নোঙর। (ছবি: জ্যোতির্ময় ও মীনাক্ষী দত্ত)



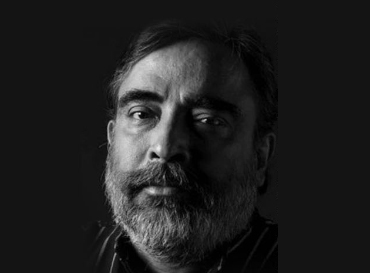
 Arts and Literature
Arts and Literature Bioscope
Bioscope Columns
Columns Green Field
Green Field Health World
Health World Interviews
Interviews Investigation
Investigation Live Life King Size
Live Life King Size Man-Woman
Man-Woman Memoir
Memoir Mind Matters
Mind Matters News
News No Harm Knowing
No Harm Knowing Personal History
Personal History Real Simple
Real Simple Save to Live
Save to Live Suman Nama
Suman Nama Today in History
Today in History Translation
Translation Trivia
Trivia Who Why What How
Who Why What How