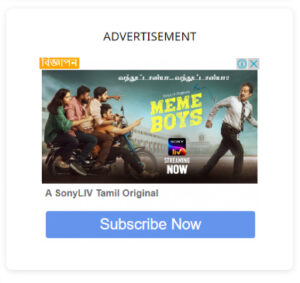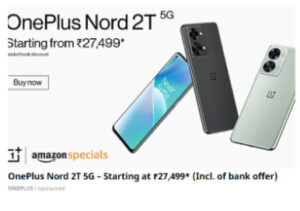- August 16th, 2022
বুদ্ধ ও নির্বাণ (পর্ব-৮)
সুমন চট্টোপাধ্যায়
‘দুঃসময়’, নাটক লিখলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। নন্দনের নিভৃত কামরায় বসে। জ্যোতিবাবুর মন্ত্রিসভা থেকে হঠাৎ রাগের মাথায় ইস্তফা দেওয়ার পরে।
সে সময়ে অনেকে অপব্যাখ্যা করেছিলেন, ‘দুঃসময়’ বলতে বুদ্ধবাবু নাকি সমকালীন বাংলার পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। একেবারেই তা নয়। এই দুঃসময়ের প্রেক্ষাপট বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার পরের উত্তর প্রদেশ। নাটকটি নিয়ে তখন বেশ হই চই হয়েছিল, সম্ভবত মঞ্চস্থও হয়েছিল বারকয়েক।
বুদ্ধবাবুর ব্যক্তিগত দুঃসময় কাটতে অবশ্য বেশি সময় লাগেনি। জ্যোতিবাবুর মন্ত্রিসভাতেই তিনি ফিরে এসেছিলেন ছয়-সাত মাসের মধ্যে। সেটাও ছিল শৃঙ্খলাপরায়ণ কোনও কমিউনিস্ট দলে একেবারেই বেনজির, ব্যতিক্রমী ঘটনা। দল ও সরকারের মুখ পুড়িয়ে কেউ এমন নাটকীয় ভাবে ইস্তফা দিয়ে ছয় মাসের মধ্যে পুনর্বাসিত হবেন, কমিউনিস্ট দলে সচরাচর এটা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে হয়েছিল। দলের নেতৃত্ব বিষয়টিকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছিলেন, এই পদত্যাগকে তাঁরা বিদ্রোহ বলে মনেই করেননি।
সে সময় জ্যোতিবাবুকে বোঝানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরে তাঁর যে রকম সম্পর্ক ছিল, পার্টির বেশি লোকের তা ছিল না। দ্বিতীয়জন অবশ্যই অনিল বিশ্বাস যাঁকেও জ্যোতিবাবু খুবই স্নেহ করতেন। আলিমুদ্দিন থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে জ্যোতিবাবু মাঝেমাঝেই জোড়া গির্জার বিপরীতে একটি বড় নার্সিং হোমের পিছনে অনিলদার অতি-আটপৌরে ফ্ল্যাটে ঢুঁ মারতেন। সবার উপরে বুদ্ধদেববাবু সম্পর্কে জ্যোতিবাবুর দুর্বলতা কিছু কম ছিল না। অনুজের আচরণে তিনি অবশ্যই আহত হয়েছিলেন, ক্রুদ্ধ হননি। সময় যেতে সেই অভিমানও গলে জল হয়ে গিয়েছিল।
জ্যোতি-সোমনাথ, জ্যোতি-অনিল, জ্যোতি-সুভাষ এই সম্পর্কগুলির রসায়ন ছিল স্পষ্ট। সোমনাথবাবুর কাছে জ্যোতিবাবু ছিলেন তাঁর ফ্রেন্ড, গাইড, ফিলোজফার। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না-করে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সোমনাথবাবু সিদ্ধান্ত নিতেন না। আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তির প্রেক্ষিতে বামেরা যখন ইউপিএ সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের ধণুর্ভঙ্গ পণ করেছে, লোকসভার অধ্যক্ষ কী করবেন তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে, সোমনাথদা দিল্লি থেকে কলকাতায় ইন্দিরা ভবনে উড়ে এসেছিলেন, ভীষ্ম পিতামহের পরামর্শ নিতে। জ্যোতিবাবু সমর্থন করেছিলেন সোমনাথবাবুর অবস্থান, যদিও তার জন্য সোমনাথবাবুকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। দল তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়ে বহিষ্কার করেছিল, সেই দুঃখ সোমনাথবাবু আমৃত্যু ভুলতে পারেননি।
সুভাষ চক্রবর্তী সজ্ঞানে নিজেকে জ্যোতিবাবুর শিষ্যের আসনে বসিয়েছিলেন, তা নিয়ে তাঁর গর্বের সীমা ছিল না। জ্যোতি-আরাধনায় সুভাষ দলীয় নিয়মকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না। প্রতি বছর ঘটা করে জ্যোতিবাবুর জন্মদিন পালন করতেন। সিপিএম-ও জানত, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, সুভাষবাবু যতই তড়পান, প্রকাশ্যে বিক্ষোভ করুন, তলেতলে দল ছাড়ার ফন্দি আঁটুন, জ্যোতিবাবুর কথার অন্যথা তিনি করতে পারবেন না কিছুতেই। সৈফুদ্দিন-সমীর পুততুন্ডদের কথা দিয়েও সুভাষ সিপিএমে রয়ে গিয়েছিলেন জ্যোতিবাবু নিষেধ করায়। সুভাষবাবুর চোখে জ্যোতি বসুই পিতা, তিনিই ধর্ম, তিনিই পরম তপস্যা।
কিন্তু বুদ্ধবাবুর সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরির সম্পর্কের রসায়ন সোজা-সাপ্টা ছিল না, মনে হত ‘কভি খুশি,কভি গম’। মুখ ফুটে পরিষ্কার করে না বললেও, বুদ্ধবাবুর বিবিধ মন্তব্য থেকে আন্দাজ করা যেত, দু’জনের সম্পর্কে কোথায় যেন একটা শৈত্য আছে, সোমনাথবাবু বা সুভাষের মতো পূর্বসূরির প্রতি তাঁর নিঃশর্ত বশ্যতা নেই। জ্যোতিবাবুর কোনও কোনও কর্মপদ্ধতি তিনি অনুমোদন করেন না। পুত্র সম্পর্কে স্নেহান্ধ পিতার আচরণেও তিনি মনে মনে বেশ বিরক্ত, বোঝা যেত। নইলে কথায় কথায় বুদ্ধদেব একদিন রসিকতা করেই বা বলে উঠবেন কেন, ‘জানেন তো, আমার একটা মস্ত সুবিধে হল, আমার কোনও ‘চন্দন’ নেই।’ আমি পাল্টা ফাজলামি করে বলেছিলাম, ‘চন্দন না থাক, নন্দন তো আছে।’
জ্যোতি বসুর জমানায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যবসায়ী তাঁর চারপাশে কার্যত একটি দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে ফেলেছিলেন, অন্তরাল থেকে এঁদের মধ্যমণি ছিলেন চন্দন বসু। আমি রসিকতা করে বলতাম পাসপোর্ট কন্ট্রোল, এদের টপকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছনো ছিল অসম্ভব ব্যাপার। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে এঁরা প্রায় সবাই যে যাঁর মতো করে আখের গুছিয়ে নিয়েছিলেন। বেশিরভাগই কলকাতার প্রাইম লোকেশনে পেয়েছিলেন সস্তায় নামমাত্র দামে বিপুল পরিমাণ জমি। ইন্ডিয়া টু ডে সে সময়ে একটি প্রচ্ছদ নিবন্ধ করেছিল বিষয়টি নিয়ে। যার শিরোনাম ছিল ‘মার্কসিস্ট ফাদার’স ক্যাপিটালিস্ট সান।’ চন্দন থাততেন দৃশ্যপটের বাইরে, তবু তাঁকে এড়িয়ে সরকারি দাক্ষিণ্য-লাভ সম্ভব হত না। জ্যোতিবাবু জানতেন সবই, মাঝেমাঝে অন্ধ পুত্রস্নেহের জন্য তাঁকে সমালোচনাও শুনতে হত। কিন্তু তিনি থাকতেন ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের মতো। সমালোচনা গায়ে তো মাখতেনই না, সময়ে সময়ে ফোঁস করে উঠতেন। ‘হ্যাঁ, আমার ছেলে ব্যবসা করে। সেটা কি অপরাধ নাকি?’ এই একটি জায়গায় তাঁর বন্ধু ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে জ্যোতিবাবুর মিল খুঁজে পাই। একজন গান্ধারি হলে অন্যজন ধৃতরাষ্ট্র।
বুদ্ধবাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে এই ব্যবসায়ীদের চরম অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। যদিও সাধারণ ভাবে শিল্পায়ন সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণায় অবিশ্বাস্য বদলও এসেছিল জমির বাস্তবতা কী বোঝার পরে। এক সময় বুদ্ধবাবু বুক বাজিয়ে বলতেন, পাঁচতারা হোটেলের তুলনায় নন্দনে তিনি অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, শিল্পপতির সান্নিধ্যের চেয়ে শিল্পী, লেখক, কলাকুশলীদের সঙ্গ তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করে। সে সময়ে বুদ্ধবাবুর এমনতর মন্তব্য নিয়ে মিডিয়ায় অনেক রঙ্গ-রসিকতাও হয়েছিল। এমনকী জ্যোতিবাবুও আমাকে জেরুজালেমের এক হোটেলে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে রসিকতা করেছিলেন, ‘আগে বুদ্ধ কেবল কালচার-ফালচার নিয়ে থাকত, এখন অবশ্য ও অনেক বদলে গিয়েছে।’ এটি ২০০০ সালের ঘটনা। ইজরায়েল থেকে মুখ্যমন্ত্রী চলে গেলেন তাঁর ‘সেকেন্ড হোম’ লন্ডনে। এটাই ছিল মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর শেষ সফর। তার কয়েক মাস পরেই সবাইকে চমকে দিয়ে হল বুদ্ধদেবের অভিষেক। (চলবে)



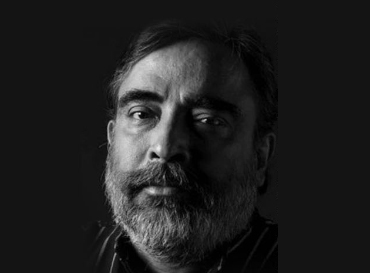
 Arts and Literature
Arts and Literature Bioscope
Bioscope Columns
Columns Green Field
Green Field Health World
Health World Interviews
Interviews Investigation
Investigation Live Life King Size
Live Life King Size Man-Woman
Man-Woman Memoir
Memoir Mind Matters
Mind Matters News
News No Harm Knowing
No Harm Knowing Personal History
Personal History Real Simple
Real Simple Save to Live
Save to Live Suman Nama
Suman Nama Today in History
Today in History Translation
Translation Trivia
Trivia Who Why What How
Who Why What How